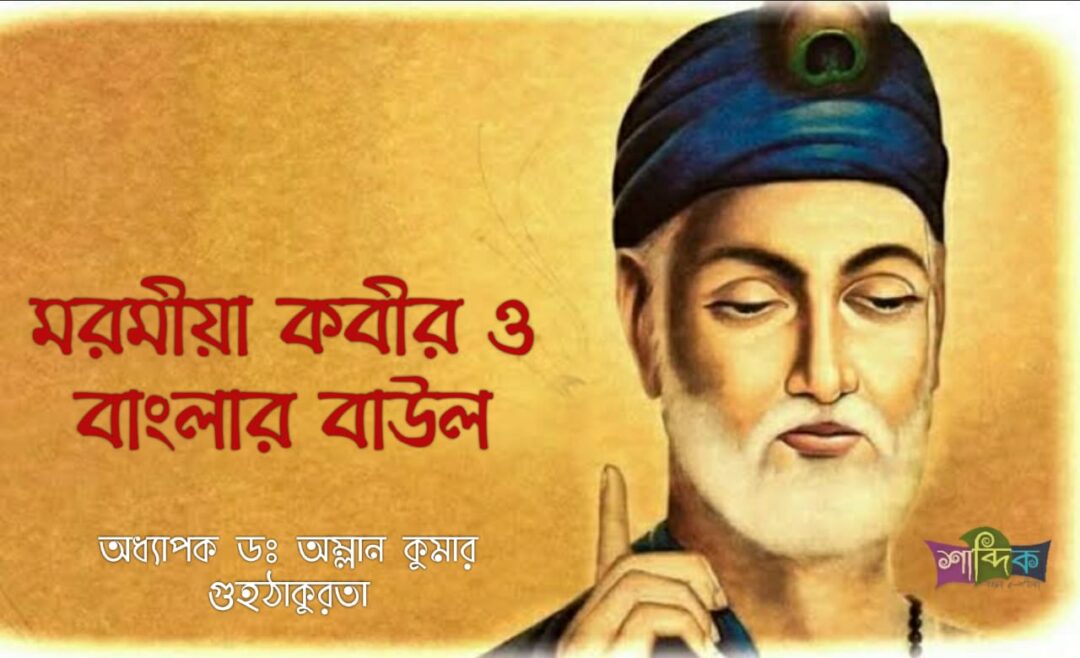
মরমিয়া কবীর ও বাংলার বাউল
ডঃ অম্লান কুমার গুহঠাকুরতাপাঠকদের পছন্দ
ভারতে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মমতের সমন্বয় :

ভারতীয় সমাজ অত্যন্ত প্রাচীন ও একইসঙ্গে তার কাঠামোও খুবই জটিল। প্রথম সভ্যতার হিসাব থেকে শুরু করলে এই সমাজ ইতিমধ্যেই পাঁচ হাজার বছর অতিক্রম করে ফেলেছে । এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহু বিদেশি মানুষের ঢেউ এসে এই সমাজের মধ্যে মিশেছে। বিভিন্ন জাতিসত্তা ও ভাষাভাষীর ঢেউ এভাবে ভারতীয় জনস্রোতে মিশে জনজীবনকে বৈচিত্রময়, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করেছে। ভারতীয় সমাজ এবং সংস্কৃতি সেদিক থেকে বিবেচনা করলে খুব গৌরবপূর্ণ।ভারতীয় সমাজে আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, শক, হুন, পর্তুগিজ, ফরাসি, মোঙ্গল, পার্সি ইত্যাদি বহু জাতি বিভিন্ন সময়ে এসেছে এবং এখানকার সংস্কৃতির রঙে রঙিন হয়ে রাষ্ট্রীয় ধারাতে বিলীন হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি, বিচারধারা, দর্শন, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদির প্রতি সহনশীলতার মনোভাব গ্রহণ করে তাদের নিজের মধ্যে বিলীন করে নিয়েছে। ভারতে হিন্দু ও মুসলিম ধর্ম মতের সমন্বয়ের শেকড় এমন গভীর ভাবে প্রথিত হয়েছে যে নানা রাজনৈতিক এবং সামাজিক উত্থান পতনে ও তাঁর কোন ক্ষতি হয় নি। ইসলাম ধর্ম এদেশে প্রথম এসেছিল শান্তিপূর্ণ পথেই, অনেক সময়ই দেশীয় হিন্দুরাজাদের উৎসাহে। পশ্চিম উপকূলের জামোরিন রাজারা মুসলমান বণিকদের তাদের রাজ্যে ব্যবসা বানিজ্যের জন্য বসবাস করতে উৎসাহিত করেছিলেন। এজন্য আনহিলওয়ারা, কালিকট ও কুইলন প্রভৃতি স্থানে তাদের বসবাসের অনুমতিও দেওয়া হয়েছিল। লোককথায় ও জনশ্রুতিতে মুঘল আমলেও রানা প্রতাপের মতো কোনও লড়াকু রাজা নতিস্বীকার করতে বেঁকে বসলেও অন্যরা মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে আপসরফা করে নিজেদের রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে তারা অনেকখানি স্বাধীনতা ভোগ করতেন।
বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য :
ভারতীয় সমাজের যে বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে, তা হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। বহু ব্যবহারে জীর্ণ এই অভিধাটিই ভারতে আত্মপরিচয়ের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুদূর অতীতে মেগাস্থিনিস (খ্রীষ্টপূর্ব ৩১৫ বছর), ফা-হিয়েন (৪০৫-১১ খ্রীষ্টাব্দ), হিউয়েন সাঙ (৬৩০-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ), আল বেরুনি (১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ), মার্কো পোলো (১২৮৮-৯৩ খ্রীষ্টাব্দ) এবং ইবন বতুতা (১৩২৫-৫১ খ্রীষ্টাব্দ) প্রমুখ বহু বিদেশি পর্যটক এদেশে এসে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে সে কথা উল্লেখ করে গিয়েছেন। ঐতিহাসিক রশিদুদ্দিন খাঁনের মতে ভারতীয় সভ্যতার মূলে রয়েছে দুটি ঐতিহ্যশালী সভ্যতার ধারা- আর্য সভ্যতার ধারা যা ভারতকে বেদের দর্শন উপহার দিয়েছে। আর একটি হল ভারতীয় ও মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি ধারা যা ভক্তি মার্গ ও ইসলামের সূফী সম্প্রদায়ের সম্মিলনে গঠিত।
ভক্তি আন্দোলন:
ভক্তি আন্দোলন প্রধাণত সমাজের নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল, তবে উচ্চশ্রেণীর ভক্ত যে ছিল না তা নয়। ভক্তি আন্দোলন ‘মুক্তি’লাভের একটি সহজ পথ যা অশিক্ষিত, অসহায় ও দুর্গতি শ্রেণীর জনগণ (Mass of the People)-কে বেশি আকর্ষণ করেছিল।শাসকের উৎপীড়নে পর্যুদস্ত মানুষ ভক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নিজেদের মানবিক অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। এই আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের নিপীড়ত মানুষজন সবলের অত্যাচারকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে কোন সফল প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত করতে না পেরে ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে সমাজে টিকে থাকতে চেয়েছিল। ‘ভক্তি’ ধারণার মধ্যে নিগূড় তত্ত্বজ্ঞানসমন্বিত অধিবিদ্যা সংক্রান্ত মতভেদ যেমন ছিল, তেমনই আবার গভীর অধিবিদ্যাসংক্রান্ত তর্ক-বিতর্ককে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে সহজ সরলভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাও ছিল। খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ থেকে অষ্ঠাদশ শতকের মধ্যে ভারতের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সব প্রান্তেই বিভিন্ন রূপে ভক্তি আন্দোলন গড়ে ওঠে। ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর ‘ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা’(১৯৩০) গ্রন্থে সুন্দরভাবে বলেছেন , মধ্যযুগের ভারতে নিপীড়িত গ্রাম-সমাজের জনগোষ্ঠী, শহরের উঞ্ছজীবি ও জীবিকাচ্যুত কারিগরদের ছিল শোষিতের ঐক্যমূলক ব্যক্তি আন্দোলন। যেমন দোর্দণ্ডপ্রতাপ রোমক সাম্রাজ্য শক্তির দাপটে দাস ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠী খ্রীষ্টের পথ ধরে শান্তি খুঁজেছিল। এ হলো রাষ্ট্রশক্তিকে মেনে নিয়েও অন্তরলোকে তা অস্বীকার করা। ভক্তি আন্দোলনের ‘ ধর্ম সমাজকে চূর্ণ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছিল’। এই লোকধর্মে ফুটে ঊঠেছিল হিন্দু-মুসলমান-শিখের দর্শন, উপাসনা ও জীবনযাপন নীতির সমন্বয়। পারস্যের সুফী সন্তগণ এই ভক্তি আন্দোলনের শিকড়ে রস সঞ্চার করেছেন। মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলিম জনগণের ভক্তিবাদী আন্দোলনের মধ্যে এক অসাম্প্রদায়িক ঐক্য গড়ে উঠেছিল – যে ঐক্যের ভিত্তি ছিল রাজসভা থেকে দূরে পীরদের দরগায়, সাধুসন্তদের আশ্রমে, মঠে, কবীর-নানক-রুইদাস থেকে শ্রীচৈতন্য পর্যন্ত ভিক্তিবাদী নায়কদের ভূমিকার তাৎপর্যে।

রামানুজ-এর শিষ্য রামনন্দ চতুর্দশ-পঞ্চাদশ শতকে প্রথম ভক্তি মতবাদ প্রচার করেন। রামনন্দ (১২৯৯-১৪১০) জন্মেছিলেন উত্তর ভারতে এলাহাবাদের কাছে, কিন্তু তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত করেন দক্ষিণ ভারতে। তিনি বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন এবং জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে ভক্তি মতবাদ প্রচার করেন। তিনি সকল মানুষের সমমর্যাদা স্বীকার করেন এবং গোঁড়া হিন্দুদের ধর্মীয় রীতিনীতি ও উৎসবাদির নিন্দা করেন। রামানন্দের অন্যতম ভাবশিয্য ছিলেন বারাণসীর সন্ত-কবি কবীর (আনুমানিক ১৩৯৮-১৪৪৮) এবং ‘রামচরিতমানস-এর রচয়িতা হিন্দী কবি ভক্ত তুলসীদাস (১৫৩২-১৬২৩)।
কবীর নিজেকে কোন বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অনুগামী বলে মনে করতেন না। নিজেকে একজন অতি সাধারণ মানুষ বলে ভাবতেন এবং ঈশ্বরের কোন বিশেষ অবয়ব আছে বলে বিশ্বাস করতেন না। তিনি কোন ধর্ম প্রচার করেননি। তিনি কোরানের মৌলবাদ এবং ব্রাক্ষ্মণ্যবাদের ধর্মীয় প্রথাকে সমানভাবে বর্জন করেন। এই সব কারণেই কবীরকে মধ্যযুগের ভারতে আধুনিকতার অগ্রদূত এবং ‘মানবতাবাদের উদ্বোধক’বলা হয়।
মরমিয়া কবীর (জীবন কথা):
প্রাচীন ভারতের একজন মরমিয়া কবি যিনি সেই সময়ে দাঁড়িয়ে হিন্দু – মুসলমান সম্প্রীতির কথা বলেছিলেন। তার রচনা ভক্তি আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করলেও তিনি আসলে প্রেমের কথা এবং জীবনের কথা বলেছিলেন যার মধ্যে প্রত্যক্ষ কোন তত্ত্ব ছিলনা। পরবর্তীকালে তার গান ও কবিতাকে সুফি ধারা এবং মরমিয়া বাদের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়।”কবীর” নামটি আরবি “আল-কবির” শব্দটি থেকে এসেছে। শব্দটির অর্থ “মহান“; এটি কুরআনে উল্লিখিত আল্লাহ্র ৩৭তম নাম।কবীর এমনি এক যুগমানব বা যুগাবতার। তাঁর আর্বিভাবকাল সমন্ধে বিশেষজ্ঞ্রা একমত নন। কবীর সম্প্রদায়ের মতে ১৪৫৬ সম্বতে (১৩১৮ খ্রীঃ) কবীরদাস আবির্ভূত হন। ‘কবীর কসৌটী’ গ্রন্থে আছে ১৫১৮ খ্রীঃ কবীরের তিরোভাব হয় এবং তিনি ১২০ বছর বেঁচে ছিলেন। এই হিসাবে ১৩১৮ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁর জন্ম হয়।
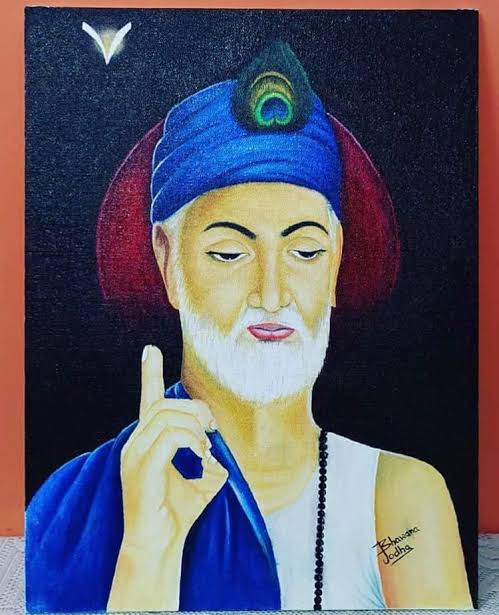
ক্ষিতিমোহন সেনের মতে রামানন্দের প্রধান শিষ্য কবীর কারিগরি সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান ছিলেন। তাঁর মতে কবীর কাশীস্থ লহরতলা নামক স্থানে ১৩৯৮ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫১৮ খ্রি. কাশীর নিকটবর্তী বস্তী জেলার মগহর গ্রামে দেহত্যাগ করেন। তিনি কবীরকে তৎকালীন দিল্লী অধিপতি সিকন্দর শাহ্ লোদীর (১৪৮৯-১৫৯৯ খ্রি.) সমসাময়িক ছিলেন বলে উল্লেখ করেন। ঐতিহাসিক আবুল ফজলও মনে করেন সিকন্দর লোদীর সময়ে কবীর জীবিত ছিলেন। অবশ্য ড. মুহম্মদ এনামুল হক কবীরের মহাপ্রয়াণ কাল উল্লেখ্য করেছেন ১৪৪৮ খ্রি.।
লোকের বিশ্বাস ছিল ১৪১০ খ্রীঃ এ রকম সময়ে গুরু রামানন্দের তিরোভাব হয়। আর সম্প্রদায়গত ঐতিহ্যানুসারে কবীরদাস গুরু রামানন্দের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছিলেন। সেই জন্য তাঁর জন্মকাল নির্দেশ করা হয়েছে ১৩৯৮ খ্রীঃ। কেননা, তা হলে গুরু রামানন্দের তিরোভাব সময় কবীরের বয়স হয় বার বছর। কিন্তু এই হিসাব ভূল। কবীরের জন্ম হয় ১৪৩০ খ্রীঃ কারণ, এঁরা মনে করেন রামানন্দের তিরোভাবের পূর্বোক্ত সন সর্ববাদিসম্মত নয়। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে গুরু রামানন্দ ১৪০০ খ্রীঃ থেকে ১৪৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তা হলে ১৪৪০ খ্রীঃ কবীরের জন্ম ও ১৫১৮ খ্রীঃ তার মৃত্যু এই মতের সম্ভাব্যতা অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কবীরের জন্ম ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দেই হোক আর ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দেই হোক তিনি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন এ বিষয় দ্বিমত দেখা যায় না। এ মতের খানিকটা ঐতিহাসিক সমর্থন পাওয়া যায়। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী এবং আবদুল হক মুহদীসের আখবর-উল-আধিয়ার গ্রন্থে কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে একেশ্বরবাদী কবীর সুলতান সিকন্দর লোদীর সময়ে বাস করতেন। সিকন্দর লোদীর রাজত্বকাল ১৪৮৯ থেকে ১৫১৭ খ্রীঃ।
অনেকের মতে তিনি জোলার ঘরে জন্মেছিলেন । জোলারা নিম্নশ্রেণীর মুসলমান। তাঁত বোনা এঁদের জাতিগত ব্যবসা। ড. হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী তাঁর কবীর গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, জোলারা মুসলমান হলেও অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে এঁদের মৌলিক ভেদ আছে। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ আর বিহারেই জোলাদের বসতি দেখা যায়। এই অঞ্চলে এক সময়ে নাথপন্থী যোগীদের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। এঁদের অধিকাংশ বাধ্য হয়ে মুসলমান হয়ে যান। এঁরাই জোলা। ধর্মের মাহাত্ম বুঝে অন্তরের তাগিদে এরা যে দলে দলে মুসলমান হয়েছিলেন তার সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই, যতটা জানা যায় এঁরা অবস্থার চাপে পড়ে মুসলমান হয়েছিলেন। কাজেই প্রথম প্রথম নূতন ধর্মও তাঁদের উপর বিশেষ কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাঁরা নামে মাত্র মুসলমান ছিলেন। পূর্বেকার অনেক ঐতিহ্য, সংস্কার, বিশ্বাস, এমন কি আচার-অনুষ্ঠান পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে থেকে গিয়েছিল। এমনি একটি জোলা পরিবারে কবীর জন্মেছিলেন এবং তখন জোলারা মনে হয় সবে মাত্র, হয়ত এক আধ পুরুষ ধরে মুসলমান হয়েছেন। কাজেই তাঁদের মধ্যে পুরোনো সংস্কার, ঐতিহ্য প্রভৃতি পুরোমাত্রাতেই বজায় ছিল। এই সবের মধ্যেই কবীর মানুষ হন। সেইজন্য তাঁর জীবনে এ সবের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর পিতার নাম নীরু, মায়ের নাম নীমা। কবীরের একাধিক পদে পাওয়া যায় তিনি নিজেকে ‘জুলাহা’ বলছেন। কাজেই এই ঐতিহ্যটিই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

কিন্তু কবীরের হিন্দু ভক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত কাহিনি টি অন্যরকম। এই ঐতিহ্যানুসারে কবীরের জন্ম হয় অলৌকিক উপায়ে। তিনি গুরু রামানন্দের জনৈক ব্রাক্ষ্মণ শিষ্যের বিধবা কন্যার সন্তান। নীরু ও নীমার তিনি কুড়ানো ছেলে। কবীরের মতো এত বড় একজন মহাপুরুষ নিম্নশ্রেনীর মুসলমান জোলা পরিবারে জন্মাবেন এ কথা তাঁদের কাছে অবিশ্বাস্য। তবে তাঁরাও স্বীকার করেন যে কবীরদাস জোলা পরিবারে মানুষ হয়েছিলেন। কবীরের অলৌকিক জন্ম সম্বন্ধে তাঁর হিন্দু শিষয়দের মধ্যে প্রচলিত একটি কাহিনী এই – গুরু রামানন্দের কাশীনিবাসী এক ব্রাক্ষ্মণ শিষ্য তাঁর বালবিধবা কণ্যাকে নিয়ে একদিন গুরুদেবকে দর্শন করতে যান। মেয়েটি প্রণাম করলে রামানন্দ তাঁকে সুপুত্র লাভ কর বলে আশীর্বাদ করেন। মেয়েটি যে বিধবা তা তিনি জানতেন না। এখন উপায়? সিদ্ধ মহাপুরুষের বাক্য ত ব্যররথ হবে না। বাপ ও মেয়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়লেন গুরুর পায়ে। গুরু বললেন আমার আশীর্বাদ অবশ্যই ফলবে। তবে ভয় নেই তোমাদের। আমি বর দিচ্ছি পুরুহ-সংঘর্ষ ব্যতীতই এই কণ্যা পুত্রলাভ করবে। জগতের পরিত্রাণের নিমিত্ত এর গর্ভে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে। অলৌকিক হবে এই সন্তানের জন্ম। সে মায়ের হাতের তালু দিয়ে ভূমিষ্ট হবে।যথা সময়ের সন্তান ভূমিষ্ট হলে মেয়েটি কলঙ্কের ভয়ে তাঁকে লহর তালাও-এ একটি পদ্মফুলের উপর রেখে দিয়ে আসে।এই অবস্থায় ছেলেটিকে প্রথম দেখতে পায় জোলা নীরু আর তার স্ত্রী নীমা। এমন সুন্দর ছেলে, না জানি কোন অভাগী ফেলে দিয়ে গিয়েছে। ছেলেটিকে নিয়ে কি করা যায় এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে অনেক সলা-পরামর্শ হল। তাঁদের নিজের কোনো ছেলেপুত্র ছিল না। তাই শেষ পর্যন্ত তারা স্থির করল ঈশ্বরই ছেলেটিকে তাঁদের দিয়েছেন। তারা ছেলেটিকে বাড়ী নিয়ে এল এবং নিজের সন্তান রূপেই পালন করতে লাগল।
কবীরের শৈশব বা বাল্যকাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। অবশ্য কোনো কাল সম্বন্ধেই সঠিক কিছু জানা যায় নি। তবে তিনি যে তখন লেখাপড়া শেখেন নি একথা নিশ্চয় করে বলা যায়। কারণ তিনিই বলেছেন, “মসী কাগদ্ ছুআ নহী” – কালি আর কাগজ ছুঁইনি।
সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত মত কবীর বিয়ে করেছিলেন। তাঁর মুসলমান শিষ্যরাও তাই বলেন। মুসলমান কিংবদন্তী অনুসারে কবীরের স্ত্রীর নাম ছিল লুই। তার একটি ছেলে ও একটি মেয় ছিল। ছেলেটির নাম কমাল, মেয়েটির নাম কমালী।
কবীরের হিন্দু শিষ্যেরা এ সব বিশ্বাস করেন না। তাদের মতে কবীরদাস কখনও বিয়ে করেন নি। লুই বলে যে কেউ ছিলেন এ কথাও তাঁরা অনেকেই স্বীকার করেন না। যাঁরা স্বীকার করেন তাঁরাও বলেন লুই ছিলেন কবীরদাসের শিষ্যা। কমাল ও কমালীও তাঁদের মতে কবীরের শিষ্য ও শিষ্যা। আবার কারো কারো মতে ওরা ঠিক শিষ্য ও শিষ্যা নয়, পালিত পুত্র ও কণ্যা।
ভারতের উদ্ভূত ধর্মের অণুসরণকারীদের মনে একটা ধারণা প্রায় বন্ধমূল হয়ে গেছে যে সন্ন্যাসী না হলে কেউ বড় রকমের সাধুসন্ত হতেই পারেন না। সেই জন্যই কবীরের মতো এত বড় একজন সিদ্ধ সন্ত, এত বড় একজন ধর্ম গুরু বিবাহিত গৃহী ছিলেন একথা তাঁদের পক্ষে বিশ্বাস করা সহজ ছিল না। তাই তাঁর নানা ভাবে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে কবীর সংসারী ছিলেন না।কবীর সংসারী ছিলেন কি না এ নিয়ে পাদ্রী কি সাহেব (Rev. Keay) বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। কবীরের পদ থেকে এ সম্পর্কে অভ্যন্তরীণ প্রমানো যা পাওয়া যায় তা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন কবীর সংসারী ছিলেন। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী প্রমুখ ভারতীয় পণ্ডিতদেরও তাই মত।
কবীরের জন্ম থেকে আরম্ভ করে নানা অলৌকিক কাহিনী তাঁকে নিয়ে রচিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুকে ঘিরেও এরকম কাহিনীর জাল বোনা হয়েছে।আমাদের দেশে একটি প্রচলিত বিশ্বাস এই যে মহাপুরুষেরা কবে দেহত্যাগ করবেন তা তারা আগে থেকেই জানতে পারেন। কবীরও তা জানতেন। সেইজন্য দেহত্যাগের কিছুদিন আগে তিনি কাশী ছেড়ে মগঘরে চলে যাবার সঙ্কল্পের কথা শিষ্যসেবকদের জানালেন। মগঘর গোরখপুরের কাছে। হিন্দুদের বিশ্বাস যে কাশীতে মরে সে-ই মুক্তিলাভ করে, অন্যত্র মরলে তা হয় না। সেইজন্য গুরুর এই সঙ্কল্পের কথা শুনে সবাই বিচলিত হয়ে পড়লেন। এই সংকল্প ত্যাগ করার জন্য সকলে মিলে গুরুজীকে অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন। কিন্তু কবীর কিছুতেই মত বদলালেন না। তিনি বললেন, স্থানবিশেষ মৃত্যু হলে মানুষের বিশেষ কোনো গতি হবে এসব কথায় কোনো যুক্তি নেই।গুরু দেহরক্ষা করবেন শুনে অন্যান্য স্থান থেকেও কবীরের হাজার হাজার হিন্দু-মুসলিম ভক্ত মঘরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সৈন্যসামন্ত নিয়ে এসেছেন রাজা বীরসিংহ। একে বলা যায় হিন্দু দলের নেতা। আর এসেছেন সসৈন্য বিজলী খাঁ। ইনি মুসলমান দলের নেতা।
কবীরের যাবার সময় হল। তিনি সবাইকে ডেকে বললেন, তোমরা এখন আর এখানে ভিড় করো না। আমি একটু ঘুমাবো। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তোমরা সব চলে যাও। রাজা বীরসিংহ বুঝলেন গুরুজীর এ শেষ নিদ্রা। তিনি এগিয়ে এসে প্রনাম করে বললেন-গুরুজী কৃপা করে অনুমতি করুন, আপনার সত্যলোকে মহাপ্রয়াণের পর আপনার পবিত্র দেহ কাশীতে নিয়ে গিয়ে আমি বিশুদ্ধ হিন্দু প্রথা অনুসারে তাঁর সৎকার করব। একথা শুনে তীব্র আপত্তি জানালেন বিজলী খাঁ। বললেন, এ কখন হতে পারে না। আমি এই পবিত্র দেহ মুসলমান প্রথানুসারে কবর দেব।
কবীর দেখলেন সমুহ বিপদ । উভয় পক্ষের সৈন্যসামন্ত প্রস্তুত, তাঁর নশ্বর দেহ নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের রক্তপাত অনিবার্য। তিনি উভয় পক্ষকে ভৎসনা করে বললেন তোমাদের প্রতি আমার এই আদেশ, তোমরা এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কোনো বাগ্ বিতণ্ডা করবেন না আর কিছুতেই পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন না। গুরুর আদেশ যে পালন করে তার অশেষ কল্যাণ হয়।দুই দলই গুরুর অন্তিম আদেশ মাথা পেতে নিল। কবীর তখন শেষবারের মতো ঘুমিয়ে পড়লেন। শিষ্যরা বাইরে থেকে কুটীরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। খানিকক্ষন পরে ঘরের ভিতর থেকে কেমন এক রকম শব্দ শোনা গেল। শিষ্যরা অঝর-নয়নে কাঁদতে লাগলেন আর গুরুজীর জয়ধ্বনি করতে লাগলেন। গুরুজী সত্যলোকে প্রয়ান করলেন। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দরজা খোলা হল। ভিতরে সে এক অপূর্ব দৃশ্য। কোথাও দেহ নেই। আছে দুখানা চাদর আলাদা করে বিছান আর প্রত্যেক চাদরের উপর একরাশ পদ্মফুল। এমনি করে কবীর হিন্দু-মুসমানের বিবাদ মিটিয়ে দিয়ে গেলেন। রাজা বীরসিংহ একখানা চাদর ও তার উপকার পদ্মফুলগুলি কাশীতে নিয়ে গিয়ে হিন্দু প্রথা অনুসারে যথারীতি দাহ করলেন। তারপর চিতাভস্ম নিয়ে গিয়ে বর্তমানে যাকে ‘কবীর-চৌরা’বলে সেই স্থানে প্রোথিত করলেন। এদিকে বিজলী খাঁ তাঁর অংশ মঘরেই কবর দিলেন। পরে অবশ্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিষ্যরা মিলে মগঘরে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। বলা বাহুল্য, বস্তুতঃ কি ঘটেছিল তা এই ধরনের কাহিনী থেকে জানবার কোনো উপায় নেই। শুধু এইমাত্র বলা যায় কবীরের পদ আলোচনা করলে তাঁর সম্বন্ধে যে ধারনা জন্মে কাহিনীটির মূল সত্য তা থেকে ভিন্ন নয়।

ভারতের সঙ্গে আরব ও ইরানের (সাবেক পারস্যের) ত্রিবিধ মিলনের ঐতিহাসিক মহাপুরুষ হচ্ছেন কবীর। তাঁরই হাতে ভারতীয় যোগ সাধন এবং অদ্বৈতবাদী সুফিদর্শনের সমন্বয় ঘটে। কবীরকে সাধারণভাবে রামনন্দের দ্বাদশ শিষ্যের প্রধান শিষ্য বলে মনে করা হয়। কিন্তু তিনি প্রধানত চিশ্তী দর্শন বা চিশ্তীয়া তরিকাভুক্ত একজন মহাপুরুষ ছিলেন। একদিকে রামানন্দ যেমন তার গুরু ছিলেন তেমনি শেখ তকী সোহরাওয়ার্দীও (এলাহাবাদের পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসী) তাঁর মুরশিদ ছিলেন। তিনি রামানন্দের নিকট থেকে ভারতীয় সাধনা পদ্ধতির সঙ্গে যেমন পরিচয় লাভ করেন তেমনি শেখ তকী সোহরাওয়ার্দীর নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে অদ্বৈতবাদী সূফী দর্শনের নিগূড় তত্ত্ব অবগত হন। অতঃপর ভীকা চিশ্তীর নিকট থেকে তিনি ‘খিরকা-ই-খিলাফত’ বা প্রতিনিধিত্বের সনদ প্রাপ্ত হয়ে অধ্যাত্ম সাধনার এক নতুন ধারা বা শাখা প্রতিষ্ঠিত করেন। সমন্বয়প্রয়াসী প্রেম ও ভক্তিপন্থী মরমীবাদের এই নতুন ধারাটিই কালক্রমে ‘সন্তধর্ম বা ‘কবীর দর্শন’ নামে পরিচিতি লাভ করে।ভারতব্রাক্ষ্মণে আছে, কবীরের জন্ম হয় ১৩১৮ খ্রীঃ এবং ১৪৯৮ খ্রীঃ তিনি দেহরক্ষা করেন।
রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের বিচারে কবীরের আবির্ভাবকালের সাধারণ নাম পাঠান আমল। এই আমলের সবচেয়ে বড় ঘটনা ভারতে মুসলমান শাসন কায়েম হওয়া এবং সেই সঙ্গে ইসলাম ধর্মের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা। ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠায় ও প্রচারে শাসকের অসিত্ত ব্যবহৃত হয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এতে পুরো সত্যটি প্রকাশিত হয়না। ভারতের আধ্যাত্ম জীবনে সত্যিকারের আলোড়ন এইসব বাহ্য অত্যাচার-উৎপীড়নের ফলে উপস্থিত হয়েছিল মনে হয় না। তার কারণ ছিল আরও গভীরতর। কবীরও ঈশ্বরের অলৌকিকত্বাকে সহজবোধ করে হিন্দু ও মুসলিম উভয়ে উপাস্য সেই এক ঈশ্বর – এটাই অধ্যাত্ম চেতনার মূলে রয়েছে বলে মনে করতেন।
কবীর দর্শন :
কবীরের জীবন রহস্যে ঢাকা। তার সঙ্গে আরও সব অলৌকিক কাহিনী জড়িয়ে আছে। মুসলমানদের আসার পরে ভারতীয় চিন্তার মধ্যে এবং ধর্মসাধনার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন এল। পাশাপাশি থাকলেও হিন্দু-মুসলমান দুই দলের ই পণ্ডিতেরা কিছুতেই দুই ধারাকে এক করতে পারলেন না। তখন নিরক্ষর সাধকের দলই উভয় সাধনাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এল। কবীর যখন হিন্দু-মুসলমান সাধনাকে উদার প্রেম ও ভক্তিভাবের মধ্যে মিলাতে চাইলেন তখন পণ্ডিতেরা বললেন, “তুই তো নিরক্ষর মূর্খ! পণ্ডিতেরা যাহা পারিলেন না, তাহা তুই কি পারিবি?” কবীর বললেন, “আমরা পণ্ডিত নহি বলিয়াই হয়ত পারিব। পণ্ডিতেরা পড়িয়া পড়িয়া পাথর বনিইয়া গিয়েছেন, তাঁহারা লিখিতে লিখিতে ঝামা ইট হইয়া গিয়েছেন। তাই দুই দলের ইটে পাথরে ঠোকাঠুকি হইলে আগুন জলে। আমরা মূর্খ, আমরা হইলাম সহজ কাদামাটি। তাই হিন্দু কাদা মুসলমান কাদার সঙ্গে সহজে মিলিবে। কিন্তু মোল্লাতে-পণ্ডিতে কখনো মিল হইবে না”।

ভারতীয় ভক্তিবাদের নব সংসস্করণে কবীরের উদাস ও উদারভাব মধ্য যুগে চিন্তা জগতের ইতিহাসে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তারই ফলশ্রুতি হল –
ভক্তি দ্রাবিড় উপজী, লায়ে রামানন্দ।
প্রগট কিয়ো কবীরনের সপ্তদ্বীপ লৈখণ্ডে।।
অর্থাৎ ভক্তি দ্রাবিড় দেশে উদ্ভূত, রামানন্দ তাকে এদেশে নিয়ে আসেন আর কবীর সপ্তদ্বীপ ও নবখণ্ডে তা প্রচার করেন।ধর্মের তথাকথিত আচার অনুষ্ঠান নিয়েই প্রচলিত ধর্মের যত সব গোলযোগ। এই প্রেক্ষাপটেই হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ সমন্বয় প্রয়াসী ‘সন্তধর্ম’তথা ‘কবীর দর্শনে-র উদ্ভব। কাজেই ধর্মের শাস্ত্রীয় আচার ও আনিষ্ঠানিকতা পরিহার করে উভয় ধর্ম দর্শনের মূলনীতি দেহপাঠ বা দেহ কর্ষণকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে ‘সন্তধর্ম। সুফিদর্শনে দেহ পাঠের মৌলিক ভিত্তি হলো প্রভু প্রেম। কবীর সূফী দর্শনের এই মূল ধারাটি গ্রহন করে ভারতীয় যোগ সাধনার সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠা করেন ‘কবীর দর্শন’। এজন্য কবীরকে বলা হয় ‘ভক্ত যোগী’বা ঈশ্বর প্রেমিক’। কবীরের ভাষায়-
পিয়া মেরে জাগে
মৈঁ কৈসে সোঈরী
রাত দিবস হমকো বোলাবে
মৈঁন সুনী রচ রহী সঙ্গ জাররী।।
কহৈঁ কবীর সুনো সখী সয়ানী
বিন প্রেম প্রিয়া মিলনে মিলানীরী।।
শ্লোকার্থ –
প্রিয়তম আমার জাগছেন, আমি কেমন করে শুই?রাত্রিদিন তিনি আমাকে ডাকছেন? আমি তা না শুনে অসতীর ন্যায়
অপরের সঙ্গে সঙ্গ করছি। কবীর বলেন, শোন গো সখী চতুরা, প্রেম বিনে সেই প্রিয়তমের মিলন মেলে না।
বিনা আকার রূপ নহি রেখা
কৌন মিলেগী আয়।
আপন পুরুষ সমঝ লে সুন্দরী
দেখো তন নিরতায়।
রাগসরূপী জির পিয়া বুঝেগ
ছাঁড়ো ভর্ম্মকী টেক
কহৈঁ কবীর আন নাই দুজা
জুগ জুগ তুম হম এক।।
শ্লোকার্থ – আকার নেই, রূপ নেই, রেখা নেই, কে এসে তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন? হে সুন্দরী, আপন স্বামীকে আজ চিনে নাও। সর্বাঙ্গ নিরত করে আজ তাঁকে দর্শন করো। আর ভ্রমকে আশ্রয় করো না।
-রাগ-স্বরূপ সেই প্রিয়তমকে বুঝে নাও।
কবীর বলেন, “দ্বিতীয় আর কেউ নেই, যুগ যুগ তুমি আর আমি এক”।
মেরী নজরমেঁ মোতি আয়া হৈ।।
অহদ গুফামেঁ সোহং রাজৈ
মুরলী অধিক বজায়া হৈ।।
সত্তলোক সত পুরুষ বিরাজৈ
অলখ সুগম দোউ ভায়া হৈ।
পুরুষ অনামী সব পর স্বামী
অপার পার জো গায়া হৈ।।

শ্লোকার্থ – আমার নয়নে তাঁর (প্রেমের) দৃষ্টি পড়েছে। অসীম গুহায় তাঁর আর আমার অভেদ বিরাজ করছে। সেখানে কী অপরূপ সুরই (তিনি) বাজাচ্ছেন। এই সত্যলোকে সত্য পুরুষ বিরাজ করেন। অলখ্য ও সুগম এই দুই রূপেই তিনি প্রকাশিত। আমার স্বামীর কোনো নাম হতে পারে না। সকলের ওপর তিনিই স্বামী। অপার-পার এই দুই সুরই তিনি গেয়েছেন।
মো কোঁ কহা ঢূঢ়ে বন্দে,
মৈ তো তেরে পাসমেঁ
না মৈ দেবল না মৈঁ মসজিদ,
না কাবে কৈ লাস মেঁ।
না তো কৌন ক্রিয়া-কর্ম মেঁ,
নহী যোগ-বৈরাগমেঁ,
খোজী হোয় তো তুরতৈ মিলি হৌঁ,
পল-ভরকী তালাসমেঁ।
কহৈঁ কবীর সুন ভাই সাধো,
স্বাসোঁকী স্বাসমে।।
শ্লোকার্থ – ওরে বান্দা, আমায় কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছিস। আমি তো তোর পাশেই রয়েছি। আমি দেউলে নেই, মসজিদে নেই,কাবাতে নেই, কৈলাসে নেই। আমি কোনো ক্রিয়া-কর্মতে নেই যোগ-বৈরাগ্যতেও নেই। যদি সন্ধানী হোস, তাহলে খুব শিগ্গিরই পেয়ে যাবি। এক পলকের খোঁজেতেই। কবীর বলছেন, ভাই সাধু, তিনি যে আছেন সব প্রাণের প্রাণে। যে-যাহোক, ভারতীয় যোগ সাধনা ও ইসলামি সূফী দর্শনের সমন্বয়ে সৃষ্টি বিশিষ্ট মানব ধর্ম কবীর দর্শন অদ্বৈতবাদী ব্যাঞ্জনায় অভিযোজিত।
বস্তুত মরমিয়া কবীর ভারত ভূমিতে মহামানবতার মিলন তীর্থ রচনা করার জন্য যে স্বপ্ন দেখেছিলেন রামানন্দ, নানক, চৈতন্য, দাদু, রজ্জব, সারাশিকো প্রমুখের ত্যাগ ও পরাকাষ্ঠার ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে লালন সাঁইজির (১৭৭৪-১৮৯০ খ্রি.) হাতে এসে তা অনেকাংশে সফল ও বাস্তবরূপ লাভ করে।
কবীর আমরণ দরিদ্রই ছিলেন। ধনী হবার ইচ্ছা পর্যন্ত হয় নি কোনো দিনই। কেন না, ধনৈশ্বর্যকে তিনি ভগবৎভক্তির ও পরমপদ লাভের পরিপন্থী মনে করতেন। এ থেকে কেউ যেন না ভাবেন কবীর শ্রমবিমূখ ছিলেন বা পরিশ্রম করে জীবিকার্জনের সঙ্গে অধ্যাত্মজীবনের বিরোধ আছে এরূপ কোনো ধারণা তিনি পোষণ করতেন। বরং তিনি পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জনের কথাই স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন –
কহে কবীর অস উদ্যম কীজৈ।
আপ জীয়ৈ ঔরনকো দীজৈ।
কবীর বলছেন, এমন উদ্যম করবে যাতে নিজেরও জীবিকা চলে অন্যকেও কিছু দিতে পারে।সময়ে সময়ে কবীর-ভগবৎপ্রেমে একেবারে আত্মহারা হয়ে যেতেন। তখন আর কাপড় বুনতেও পারতেন না। তাঁর পদেই একথার উল্লেখ পাওয়া যায়।
সদানন্দ মানুষ ছিলেন কবীর। কিন্তু তাই বলে তার মধ্যে কোনো রকম ভাববিহ্বলতা বা দুর্বলতার চিহ্নমাত্র ছিল না। স্থির ও প্রখর ছিল তাঁর বুদ্ধি। অনমনীয় ছিল তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা। বিশেষ বিবেচনার পর একবার তিনি যা সত্য বলে গ্রহণ করতেন কিছুতেই তা থেকে বিচ্যুত হতেন না। কবীরের আরেকটি বিশেষত্ব ছিল, তিনি ছিলেন বিচারশীল মানুষ। বিনা বিচারে তিনি কিছুই গ্রহণ করতেন না। “তিনি সত্যকে পরখ করিয়া লইতেন”।যেমন একটি পদে আছে, ‘দেহ ধরেকা দণ্ড হৈ সব কাহূকো হোয়’–দেহ ধারণা করাটাই দুঃখ। এই দুঃখ সবাইকে ভোগ করতে হয়। অন্য একটি পদে তিনি বলছেন, ‘তন ধরি সুখিয়া কোই ন দেখা জো দেখা সো দুখিয়া হো’। – দেহধারী কাউকে সুখী দেখলাম না। যাকে দেখি সে-ই দুঃখী। কবীর যে দুঃখ ও অশান্তিতে অবিচলিত থাকেন তাঁর এই মনোভাবও তার অন্যতম কারণ বলা যায়। কিন্তু আসল কারণটি তিনি স্বয়ং নির্দেশ করেছেন – “সুখ-দিখকে ইক পরে পরম সুখ তেহিমেঁ রহা সমাঈ”। – সুখ দুঃখের পরে এক পরম সুখ, তারই মধ্যে প্রবেশ করে থাকি।
তিনি ছিলেন খাঁটি মানুষ এবং ভক্তিমার্গীর পক্ষে আশ্চর্য রকমের যুক্তিবাদী।তিনি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকের ঘরে মানুষ হয়েছিলেন বা জন্মেছিলেন। সেইজন্য শুধু জাতিভেদের জন্য মানুষের কি পরিমাণ অপমান হতে পারে, মানুষ মানুষকে কতদূর ঘৃণা করতে পারে তা তিনি প্রত্যক্ষভাবে জানতে পেরেছিলেন।
কিন্তু এই সত্য প্রচার করতে গিয়ে প্রচলিত ধর্ম ও সমাজের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে। আর তার জন্য তাঁকে কম লাঞ্ছনা ও নির্যাতন ভোগ করতে হয় নি।কবীর হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মেরই বাহানুষ্ঠানকে আক্রমণ করেছেন। তিনি বেদ-কোরাণ, পুরোহিত-মোল্লা, মন্দির-মসজিদ, তীর্থ-হজ, ব্রতোপবাস-রোজা, সন্ধ্যাহ্নিক-নমাজ কিছুই মানতেন না। এ সমস্তই নিরর্থক মনে করতেন। এইজন্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তাঁর উপর খড়গহস্ত হয়ে উঠে। কবীরকে এমনি জব্দ করতে না পেরে শেষে হিন্দু-মুসলমানে মিলে সুলতান সিকন্দর লোদীর কাছে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করেন। এ সমন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। তবে তার সব কটিরই সার কথা এক। মুসলমান বললেন – জাঁহাপনা, কবীর আমাদের ধর্ম নষ্ট করল। হিন্দুও করলেন ঐ একই অভিযোগ। সব শুনে সুলতান হুকুম দিলেন, কবীরকে হাজির কর দরবারে। হুকুম তামিল হল। কবীরের সঙ্গে সুলতানের অনেক বাগ্বিতণ্ডাও হল। তার কড়া কড়া কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন সুলতান। কবীরের প্রাণদণ্ড হল। কিন্তু সুলতান তাকে বধ করতে পারলেন না। জলে ডুবিয়ে আগুনে পুড়িয়ে হাতির পায়ের তলায় ফেলে দিয়ে কত রকমেই না চেষ্টা করা হল কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেষে সুলতানের চোখে ফুটল। কবীরের অলৈকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন সুলতান সিকন্দর লোদী।
কবীর ও বাউল চিন্তাধারা:

দেহের সাধনার মধ্যে দিয়েই দেহাতীতকে পাওয়া সম্ভব। প্রেম যতক্ষণ না নির্মল নিকষিত হেম হয়ে ওঠে ততক্ষণ সাধনা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না। বৈদিক মতে এই শুদ্ধ প্রেমতত্ত্ব স্বীকৃত হয়। বাউলেরা এই বৈদিকতার ধার ধারেন না।
“কাম প্রেম রতি হবে এক ঠাঁই
সুখ দুঃখ আদি তথায় কিছু নাই,
নির্মল সে পথে হাউড়ে চায় যেতে
এই শক্তি আত্মশক্তি হলে যায় দর্শন।।”
(বাঙালির ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি – রমাকান্ত চক্রবর্তী। পৃ. ৯৯)
অশুদ্ধ মন নিয়ে এবং কাম মিশ্রিত রতি নিয়ে কখনই এই সাধনা করা যায় না। এইভাবে সাধনা করতে থাকলে সাধনার একটি স্তরে এসে কাম চলে যায়, শুধু প্রেমই থাকে। এইভাবে বিষে বিষক্ষয় করতে হবে।
“যেমন এক গাছেতে হয় দুই রকমের ফুল
লাল আর শ্বেতেতে হয় সমতুল
কাম আর প্রেম এই রূপ দুই জনা।
কাম লোহা, প্রেম কাঁচা সোনা
ননী যেমন দুগ্ধের সার।”
(বাঙালির ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি – রমাকান্ত চক্রবর্তী। পৃ. ১০০)
কবীরের দর্শনচিন্তার সঙ্গে বাউল চিন্তাধারা র অনেক মিল রয়েছে । ‘যা আছে ভাণ্ডে, তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে’ এই আপ্তবাক্যে বাউলও বিশ্বাসী। অর্থাৎ এই দেহ ভাণ্ড হলো এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অণু সংস্করণ। এমনটি ভাবার কারণ হলো এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যে সব ভৌতিক পদার্থ দ্বারা তৈরি এই দেহ সেই সব পদার্থ দ্বারা তৈরি। অর্থাৎ এই মানব দেহ এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উভয়ই আব, আতস, খাক, বাত ও ব্যোম – অর্থাৎ আগুন, পানি, মাটি, বাতাস ও আকাশ দ্বারা তৈরি। তাই যৌক্তিকভাবে বাউলগণ ও তান্ত্রিকগণ এই দেহকে ব্রহ্মাণ্ডের অণু সংস্করণ বলে থাকে। বাউল হৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে ডাক দিয়েছে মানুষকে। সেই তার ধ্যানের মন্ত্র, সেই তার মানব –উপাসনা।“ ভাবের আজগুবি কল গৌরচাঁদের ঘরে, সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের খবর, আনছে একতারে, গো সখী, প্রেমতারে”- (বাউল গান )। বাউল শ্রেণী বিভক্ত সমাজে বিশ্বাস করে না। সে বিশ্বাস করে অখণ্ড মানব সমাজে। বাউল মতে শুদ্ধ প্রেমের প্রেমী যাঁরা হল তাঁদের চোখ দেখলে চেনা যায়। জীবাত্মার মধ্যেই পরমাত্মার স্থিতি। যে নিজেকে চিনেছে, সে পরমাত্মাকে জেনেছে। আত্মা পরমাত্মার অংশ, কাজেই দেহের মধ্যে আত্মাকে খুঁজে ফেরাই বাউলের সাধনা, তাঁদের ব্রত। উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বাউল গানের সংগ্রহ, মুদ্রন এবং আলোচনা শুরু হয়। বাউল দর্শন সম্পর্কে লালন বলেছেন, “মানুষতত্ত্ব”। ভাববাদী দর্শন ইহজগৎ এবং দেহী মানুষকে নশ্বর, মায়া বলেছে। তাদের কাছে বিদেহী সত্তা, আত্মা, স্বর্গ গুরুত্বপূর্ণ। বাউলের কাছে ইহ-দেহ সত্য। অন্যগুলি কাল্পনিক অনুমান মাত্র। ‘যারা মানুষকে সত্য বলে মানে, তারা বিদেহী সত্তাদের কাল্পনিক জগতকে অগ্রাহ্য করে’ (লালন সাঁই এর গান, কবিতা পাক্ষিক, ২০০৫, পদ নং ৩৬)। পীড়ন, শোষণ এবং মানবতা বিরোধী আন্দোলনের চিহ্ন লেগে আছে বাউল গানে।

বিশেষত জাতপাতের নামে অস্পৃশ্যদের মানবিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে বাউলগান তো সোচ্চার। মুসলমান সমাজেও হীনবৃত্তির মানুষেরা যে অমর্যাদা পায়, তার প্রতিবাদ করেছেন দুদ্দু, “জোলা কলু জাদার যারা ইতর জাতি বলয় তারা”। দুদ্দু বাউল এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে – ‘যে খোঁজে মানুষে খোদা সেই তো বাউল /বস্তুতে ঈশ্বর খুঁজে পায় তার উল।।/পূর্ব পুনর্জন্ম না মানে চক্ষু না দেয় অনুমানে /মানুষ ভজে বর্তমানে, হয়রে কবুল’ (পদ নং ৮২) ।‘আমি’র অহং বা স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়েই বিশ্বপ্রেমের সঙ্গে একাত্ম হয়েই সে ভুবনে পৌঁছতে হয়। অযথা ‘আমি, ‘আমি’ করলে শুধু সময় যায় এবং নিজের চারদিকে বেড়া-ই বাঁধা যায়। বাউল ত্যাগী-উদাসী- আত্মানুসন্ধানী মানুষ একজন। ‘যা আছে ভাণ্ডে, তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে’ এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাসীও। বাউল হৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে ডাক দিয়েছে মানুষকে। সেই তার ধ্যানের মন্ত্র, সেই তার মানব –উপাসনা। এখানে একটি প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কবীরের রচনার মধ্যে ভক্তি ও ভাবুকতা যতটা ছিল ততটা কবিত্ব ছিল না। মূলতঃ ছিলেন ভক্ত সাধক, কবিত্ব যে তাঁর রচনায় থাকবে না এটাই স্বাভাবিক তবু তাঁর আধ্যাত্মিক রসে ভরা কলসী থেকে ছলকে পড়ে কাব্যের কৌটোতেও কম রস জমেনি।কবীর তাঁর অসংখ্য দোঁহা/বাণী-র মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্যের বিরোধিতা করেছেন। যে অর্থে আমরা আখ্যায়িত করি সে অর্থে কবির রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বা রাষ্ট্রদার্শনিক ছিলেন না কখনোই। কিন্তু তিনি জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে তাঁর দোঁহার মাধ্যমে নিপিড়ীত শ্রমজীবী মানুষদের স্বাধীন সত্বার জয়গান করেছেন। যার ভিত্তি ছিল ভক্তি। তাঁর মতে ভক্তিই হলো এইসব অসাম্যের প্রতিবাদের হাতিয়ার। কবীরের মৃত্যুর প্রায় ৭৫ বছর পরে তাঁর অনুগামীরা তাঁর সমস্ত দোঁহাগুলিকে একত্রিত করে গ্রন্থ হিসাবে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। মঠ স্থাপন করে সন্ত কবীরের ধ্যাণ ধারণা প্রচার করেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ভানুদাস, জগুদাস, ধরম দাস ও আরো অনেকে। কবীর স্বয়ং কিছুই লেখননি বা লিখিয়ে যান নি। ফলস্বরূপ পরবর্তীকালে অনেক গ্রন্থে বা ‘বীজক-এ কবীরের বাণী বা দোঁহা-র নামে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে কবীরের প্রভাব এতটাই বিস্তার লাভ করেছিল যে উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে বা জাতপাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সময়ে অনেক বাণী বা দোঁহা কবীরের নাম করে চালানো হতো।
মন না রঙ্গায়ে রঙ্গায়ে জোগী কপড়া।
আসন মারি মন্দিরমে বৈঠে। ব্রক্ষ্ম ছাড়ি পূঞ্জন লাগে পথরা।।
কনবা ফড়ায় জোগী জটবা বঢ়ৌলে। দাঢ়ী বঢ়ায় জোগী হৌই গৈল বকরা।।
জংগল জায় জোগী ধুনিয়া রমৌলে। কাম জরায় জোগী হোয় গৈলে হিজরা।।
মথবা মুঁড়ায় জোগী কপড়া রঙ্গৌল। গীতা বাঁচকে হোয় গৈলে লবরা।।
কহহিঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো। জম দরজবা বাঁধল জৈবে পকড়া।।
দোঁহা -র বাংলা:
যোগী, মন না রঙ্গিয়ে কাপড় রঙ্গালি। আসন করে বসলি মন্দিরে। ব্রক্ষ্মকে ছেড়ে পূজো করতে লাগলি পাথরের। ওরে যোগী, কান ফুটো করলি, জটা রাখলি আর দাড়ি রেখে হয়ে গেলি ছাগল। জঙ্গলে গিয়ে ধুনি জাললি, রে যোগী, কামকে জীর্ণ করে হয়ে গেলি হিজড়া। যোগী রে, মাথা মুড়ালি, কাপড় রঙ্গালি আর গীতা পড়ে হয়ে গেলি মিথ্যাবাদী। কবীর বলছে, সাধু রে ভাই, তোকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাখবে যম দরজায়।
প্রাসঙ্গিকতা:
পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, কবীর ছিলেন আত্মজ্ঞ সিদ্ধপুরুষ। তিনি জানতেন, পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, তত্ত্বালোচনা, নিয়ম-ব্রত পূজা এসব উপলক্ষ্য মাত্র। এসবের লক্ষ্য আত্মাজ্ঞান লাভ বা ভগবৎপ্রাপ্তি। কিন্তু ধর্মপথে যাঁরা চলেন তাঁরাও বেশীর ভাগ এ কথা ভুলে যান। তাঁরা লক্ষ্য ভুলে গিয়ে উপলক্ষ্যকেই মুখ্য করে তোলেন। অনেকে মনেকরেন এই সব উপলক্ষ্যের চর্চা করা আর লক্ষ্যে পৌঁছান একই কথা। এইজন্য, অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা উপলক্ষ্যের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়েন, লক্ষ্যে আর পৌছাতে পারেন না। সাধারণ মানুষ এ সব ব্যক্তিকে খুব ধামিক বলে মনে করে,ভাবে এঁরা বুঝি সিদ্ধিলাভ করেছেন। মরমিয়া কবীর ছিলেন আত্মবিদ্। পুথি পড়তে না পারলেও শাস্ত্র তথা ধর্মের যথার্থ মর্ম তিনি জেনেছিলেন। কাজেই এই ধরণের আঘাত করার অধিকার তাঁর ছিল। যেখানেই তিনি দেখেছেন মানুষ্য লক্ষ্য ভুলে উপলক্ষ্যকেই মুখ্য করে তুলেছে, যেখানেই দেখেছেন সত্যের নামে মিথ্যার বেসাতি চলেছে, চলেছে ভণ্ডামি, সেখানেই তিনি খড়গহস্ত হয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি হিন্দু-মুসলমান কাউকে রেহাই দেন নি।
বাউলরা প্রচলিত ধর্ম, জাতি বা বর্ণবৈষম্য, দেবদেবী, পূজা-আচার, নামাজ-রোজা, মন্দির-মসজিদ কন্টকিত সামন্ত সমাজের ধ্যানধারণাকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করতেন, এবং সেই ভাবধারাতেই আপ্লুত তাঁদের ‘মনের মানুষ’ এক নতুন মানবতাবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। সামন্ত সমাজে নিপীড়িত জনমানসে তাই সেই মানুষটি আসন পাততে পেরেছিল। সমাজের অতি দরিদ্র ভূমিহীন নিঃস্ব চাষী ও তথাকথিত নিম্নজাতি থেকেই বাউলরা এসেছিলেন। বাউল দর্শন মানবমুখী, ইহজীবনমুখী, তবু কেন তারা বিবাগী, কেন নিজেরা বলে : ‘আমরা পাখির জাত।’ তার কারণ আচার-বিচারের প্রহরী-ঘেরা বর্ণহিন্দুর সমাজের অচলায়তনে মুক্তমতি বাউলদের বাসা বাঁধবার কোনো সুযোগ ছিল না। এই ‘মুক্ত ডানা’ পাখির জাত ছিল সামন্ত্রতন্ত্রী শেকলে বাঁধা মেহনতকারী মানুষের মুক্তি-কামনারই প্রতীক ও প্রতিনিধি। বাউলদের নৈরাশ্যবাদ এক অর্থে মানবতাবাদের পরিপোষক।

কবীরের কাছে ভগবান্ পুঁথির কথামাত্র, তত্ত্বমাত্র ছিলেন না। তাঁর কাছে ভগবান্ ছিলেন প্রত্যক্ষ সত্য। এইজন্য পুথিপড়োর সঙ্গে তাঁর বনতা না। একটি পদে তিনি বলেছেন – ‘ওরে তোর মন আর আমার মন কি করে এক হবে? আমি বলছি চোখে দেখি আর তুই বলছিস পুঁথিতে লেখা আছে’। পাঁড়েজীর ‘বেদ-কিতাব সম্বন্ধে কবীরের যে-মত মৌলানা সাহেবের ‘কোরাণ কিতাব’ সম্বন্ধেও সেই মত। তার কারণ, এইসব পুঁথিপড়োদের দেখে দেখে তাঁর ধারণা হয়েছিল পুঁথি ভগবান্ কে আড়াল করে দেয়। পুঁথিপড়োরা পুঁথিকেই জানে ভগবান্ কে জানে না।কবীর দেখেছিলেন লোকে মূল লক্ষ্য ভুলে গিয়ে ধর্মের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান পালনকেই ধর্ম মনে করছে। বেশীর ভাগ লোকেই এ সবের পিছনের তত্ত্ব কি তা জানত না, আর পাঁচজনে যামানে অন্ধভাবে তাই মেনে চলত। ধর্মাচরণ তাঁদের কাছে একটা জড় অভ্যাসমাত্র ছিল।এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায় কবীরের পদেই। যে সব ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু বা মুসলমান ধর্মের বাহ্যাচার খণ্ডন করেছেন, সেই সব ক্ষেত্রে সর্বত্রই মনে হয় তিনি ঐ সব বাহ্যাচারের সমর্থক ও প্রচারক পণ্ডিত, পাঁড়ে, কাজী বা মোল্লাকে নিত্যন্ত মূর্খ ভেবেছেন।মোল্লা আজান দেন, চেঁচিয়ে ডাকেন আল্লাকে। কবীর দিলেন তাঁকে এক খোঁচা। বললেন – ‘মোল্লা হয়ে যে আজান দিস, তোর আল্লা কি কালা? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের পায়ে নূপুর বাজে তাও যে প্রভু শুনতে পান। সাধু-সন্ন্যাসীরা জটা রাখে, মাথা মুড়ায়, গায়ে ভস্ম মাখে, সন্ধ্যাহ্নিক করে, মূর্তিপূজা করে। কবীর বলেন – যদি এ সবের পিছনে তত্ত্ববিচার না থাকে, যদি এ সবের দ্বারা ভগবান্ কে না পাওয়া যায় তবে এ সব দিয়ে কি হবে? তিনি মন্দির-মসজিদ এ সবের বিরোধী ছিলেন। কবীর প্রশ্ন করেছেন যদি খোদা থাকেন মসজিদে, তবে বাকী জগৎটা কার? উত্তরও নিজেই দিয়েছেন – ভগবান্ বা রাম সব জগৎ জুড়ে আছেন, আছেন অন্তরে। মূর্তি,তীর্থ এ সমস্তই তো তাঁর মধ্যে রয়েছে। এই জন্য সকল প্রকার হিংসার তিনি ছিলেন একান্ত বিরোধী। বিশেষ করে ধর্মের নামে পশুহত্যার তিনি তীব্র নিন্দা করেছেন। শাক্ত পাঁড়েকে তিনি নিপুণ কসাই বলেছেন। বলেছেন পাঁড়ে এক পলকের মধ্যে রক্তের নদী বহিয়ে দিয়ে নিজের আত্মাকেই বধ করে। মুসলমানের গো-কোরবানিরও তিনি একই রকম নিন্দা করেছেন। মরমিয়া কবীর আপন মতের সমর্থনে টিয়া পাখীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। লোকে টিয়া পাখী পোষে তাকে হরি হরি, রাম রাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, এমনি কোনো নাম বলতে শিখায়। মরমিয়া কবীর বলেন, “টিয়া পাখী যতক্ষন মানুষের সঙ্গে থাকে ততক্ষণ হরি হরি বলে কিন্তু তার উপর হরিনামের কোনো প্রভাব পড়ে না। তাই, যদি কখনো সে জঙ্গলে উড়ে চলে যায় তা হলে সে নামের কথা তার আর মনেই পড়ে না।কবীর মনে করতেন মানুষের মধ্যেও আছে এমনি অনেক টিয়া পাখী। তারা মুখে রাম রাম করে কিন্তু তাদের মন পড়ে থাকে বিষয়ের মধ্যে। এই সব লোকের অন্তরে যথার্থ প্রেমভক্তি জন্মায় নি। তাই,মুখে রাম-নাম করলেও তাদের মুক্তি হয় না। একটি পদে বলেছেন, “পূজা করি না, নমাজ পড়ি না, হৃদয়ে এক নিরাকারকে নমস্কার করি”। যাঁরা মূর্তিপূজা করেন তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন, “ নিজের হাতে মূর্তি বানিয়ে দুনিয়া তার কাছে ফল চায়”। বলেছেন, “সত্য সৃষ্টিকর্তা যিনি তিনি এই সমস্ত জগতের মধ্যেই আছেন, মূর্তির মধ্যে নেই”। জাগতিক মানুষের চোখে বাউল বিবাগী, কিন্তু নিজেদের কাছে তারা মুক্তি-সন্ধানের পথিক। তারা নিজেদের মুক্ত থেকে অন্যদের মুক্তির পথ দেখায়। মুক্তির পথের দিশারী হল ‘মনের মানুষ’। মনের মানুষের অনেক নাম। সাধক কখনো বা তাঁকে খাঁচার ভিতর ‘অচিন পাখী’ বলেন, কখনো বা বলেন ‘আলেখ সাঁই’, কখনো বা তিনি ‘লাশরীকালা’, আবার কখনো বা তিনি সেই, “আরশী নগরের পড়শী।” সাধক লালন সাঁই সর্বত্রই তাঁকে এমন এক পরিবেশে দাঁড় করান যে, তাঁকে জীবলোক বিহারী পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই ভাবতে পারা যায় না। এ যেন রবীন্দ্র–কাব্যের সেই রহস্যময় ‘জীবন-দেবতা’, যিনি শেষ পর্যন্ত ভক্তের হৃদয় অরণ্য থেকে মুক্ত হয়ে ‘বিশ্বদেবতায়’ রূপান্তরিত হয়ে যান। বলা যেতে পারে কবীরের দর্শনচিন্তার সঙ্গে বাউল চিন্তাধারার এ এক অদ্ভুত সমাপতন ।।




























