
মহামৃত্যুর রুদ্র সঙ্গীত
রুদ্র প্রাসাদ সিনহাপাঠকদের পছন্দ
মহামৃত্যুর আহ্বানে বাঙালি বিপ্লবীরা (পর্ব ১):
মৃত্যু নিশ্চিত। আমাদের সকলের জীবনের অন্তিমে মায়াবী আলোর মত মৃত্যু জেগে থাকে। কিন্তু অনিশ্চিত তার আগমন ক্ষন। এই অনিশ্চয়তা ই সাধারণ মানুষ কে দেয় বেঁচে থাকার আনন্দ। জীবনানন্দ র ভাষায়
কখন মরণ আসে কে বা জানে
কালীদহে কখন যে ঝড়, কমলের নাল ভাঙে
আর যখন মৃত্যুর দিন , ক্ষন স্থির হয়ে গিয়ে তা মানুষ কে নিতে আসে কজন পারে তাকে পরম আত্মীয়ের মত আপন করে নিতে? যারা পেরেছিলেন সেই মহামৃত্যুকে স্বাগত জানাতে নিজ মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য; ধারাবাহিক ভাবে শোনাবো তাদের মৃত্যু–প্রেমের কথা আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রী ভাই বোন দের। এইসব জীবন উত্তরাধিকার সূত্রে তোমাদের ই তো প্রাপ্য। প্রাথমিক ভাবে তুলে ধরবো সেইসব মৃত্যু উপাসক দের কথা যারা অল্প পরিচিত অথবা একেবারেই অপরিচিত।
মহামৃত্যুর আহ্বানে (পর্ব ২)
১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রহের পর সারা ভারত জুড়ে নেমে এলো নির্মম অত্যাচার ও মৃত্যুভয় এর দর্শন। ইংরেজ ভাবলো মরণের ভয় দেখিয়ে স্তব্ধ করে দেবে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ঢেউ। কিন্তু ফল হলো উল্টো। দেশপ্রেম ও আদর্শ নিষ্ঠার সামনে ম্লান হয়ে যেতে লাগলো মৃত্যুর করাল বদন। শহীদ ভবানী ভট্টাচার্যের উপমায় ” অমাবস্যার শ্মশানে ভীরু ভয় পায়। সাধক সেখানে সিদ্ধিলাভ করে ।” মৃত্যু যেন হাসি খেলা গানের মত স্বাভাবিক হয়ে উঠলো কিশোর যুবক বিপ্লবীদের কাছে। ইউরোপীয় হাংমান (ফাঁসুড়ে) ক্যারী বলেছেন “স্বদেশীদের ফাঁসী দেবার সময় তাদের ঠাট্টা তামাশা আমাকে খুব haunt করে। এতে আমার মদের খরচা বেড়ে যায়।” বাংলায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চক্রবর্তী । ১৯০৭ এর শেষ বা ১৯০৮ এর শুরু। প্রফুল্ল বিপ্লবের প্রয়োজনে বোমা তৈরি করলেন। দেওঘরের দিঘিরিয়া পাহাড়ের বন জঙ্গল ভেদ করে চূড়ায় উঠছেন প্রফুল্ল ও তার চার সাথী। সাথীদের মধ্যে আছেন বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, নলিনী কান্ত গুপ্ত ও বিভূতিভূষণ সরকার। চূড়ায় একটি বড় পাথর নির্বাচন করা হল। তার একদিকে খাড়া খাদ। অন্যদিকে ঢালু। ঠিক হলো পাথরের উপর থেকে ঢালুদিকে বোমা নিক্ষেপ করে পরীক্ষা করা হবে। কিন্তু ছুঁড়তে গিয়ে অদূরেই ফাটল বোমা। সেখানেই নিহত হলেন প্রফুল্ল। জখম হলেন উল্লাসকর। প্রফুল্ল চাইতেন সশস্ত্র প্রতিরোধ ও বীরের মৃত্যু। তাই তিনি পেলেন। বিপ্লবের স্বার্থে একথা গোপন রাখতে হবে। তাই সাথীরা ওপরে জঙ্গলের মধ্যে এক পাথরের পাশে প্রফুল্লর মৃতদেহ লুকিয়ে রেখে নিঃশব্দে নীচে নেমে এলেন। একজন দুঃখ করে বললেন আমরা পাঁচজন ওপরে গেলাম আর ফিরছি চারজন। বারীন বললেন “চুপ কর। আবেগ দমন কর। আমরা শোকাহত হলেও পুলিশ সন্দেহ করবে।” প্রফুল্লর স্বপ্নই সাথীদের কাছে প্রফুল্ল কে হারানোর বেদনার থেকে বড় হয়ে উঠলো। গোপনে বারীন প্রফুল্লর পিতাকে এই নিদারুণ দুঃসংবাদ দিলেন। পিতার চোখে জল। পর মুহূর্তে নিজেকে সামলে বারীনের কাঁধে হাত রেখে বললেন ” তোমরা দুঃখ কোরো না। আমার আর একটি ছেলে আছে। তার নাম সুরেশ। তাকেও আমি উৎসর্গ করবো দেশের কাজে। “
মহামৃত্যুর আহ্বানে (পর্ব ৩)
১০ ই নভেম্বর ১৯০৮; হেমন্তের ভোররাত্রি। ফুল আর ঘাসে ঘাসে শিশিরের স্পর্শ। সুরভিত বাতাসের আদরে ডুবে থাকা পৃথিবীকে শেষ বিদায় জানালেন কানাই লাল দত্ত। আলিপুর বোমার মামলায় বন্দী ছিলেন আলিপুর জেলে। নরেন গোস্বামী রাজসাক্ষী হয়েছে । ক্ষতি হচ্ছে বিপ্লবী কর্মকান্ডে। কাঁঠাল খাবার ইচ্ছা হলো কানাই এর। ইঙ্গিত বুঝে কাঁঠালের ভেতর রিভলবার পাঠিয়ে দিলেন বারীন, বসন্ত ও মতিলাল। নরেন গোস্বামীর কাছে খবর গেলো কানাই অনুতপ্ত । সেও রাজসাক্ষী হতে চায়। ডিস্পেন্সারি ঘরে বৈঠকের ব্যবস্থা হলো। বৈঠক এর স্বাগত ভাষণ দিলো রিভলবার। গর্জে উঠলো সে কানাইয়ের হাতে। নরেন গুলিবিদ্ধ হয়ে পালাবার চেষ্টা করল। ছুটে গিয়ে আরো গুলি করে নরেনের মৃত্যু নিশ্চিত করলেন কানাইলাল। জেলে বন্দী অবস্থায় রাজনৈতিক হত্যা। শাস্তি নির্ঘাত মৃত্যুদন্ড। পরোয়া করলেন না কানাইলাল। তার আগে অনেকগুলি action ব্যর্থ হয়েছিল। তা দেখে কানাইলাল আক্ষেপ করে বলেছিলেন “action ব্যর্থ হছে কারণ action এর থেকে পালানোর দিকে বেশি নজর। আমি যখন actoin করবো PM (পলিটিকাল মার্ডার) নিশ্চিত করবো। নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য লালায়িত থাকবো না।” তাই করেছিলেন 22 বছরের কানাইলাল দত্ত। নরেন গোসাঁই এর হত্যা বিপ্লবী কর্ম কান্ড কে রক্ষা করেছিল বহুলাংশে। কিন্তু এর ফলস্বরূপ কানাইলাল এর ফাঁসি হয়ে গেলো। তার মৃত্যুর আগে কোনো অনুশোচনা ছিল না। উকিল নিতে বা মৃত্যুদণ্ডের আদেশ রদ এর অনুরোধ করতেও অস্বীকার করেছিলেন। সেলের ভেতর বুক চিতিয়ে মাথা তুলে হাঁটতেন কানাই। শিবনাথ শাস্ত্রী কানাই এর ফাঁসির দুদিন আগে অন্য এক বিপ্লবী র সঙ্গে দেখা করতে এসে কানাই কে দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। পরে বলেন “কানাই কে দেখলাম। কি তেজ। যেন পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ। ওকে আশীর্বাদ করতে হলে আমাকে তিন জন্ম সাধনা করতে হবে। ” মৃত্যুর আগের দিন দাদা আশুতোষ দত্ত ভাই এর সঙ্গে দেখা করতে এসে তার চশমা টি চান স্মৃতি হিসাবে রেখে দেবার জন্য। কানাইলাল বলেন ” না দাদা । চশমা দেয়া যাবে না। কারণ চশমা না থাকার কারণে যদি আমি হোঁচট খাই ওরা (ইংরেজ) ভাববে ভারতীয় রা ভীতু। ফাঁসির নাম শুনে ভয় পেয়েছে।” তাঁর ইচ্ছা ছিল তার মৃতদেহ নিয়ে মিছিল বেরোক যাতে তার মৃতদেহ দেখে ছাত্র যুবক দের সত্ত্বা জেগে ওঠে। নিজের মৃতদেহ কেও তিনি দেশের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তার মৃতদেহ নিয়ে বিশাল মিছিল হয়েছিল। ইংরেজ এর বুক শুকিয়ে গিয়েছিলো গণ অভুথান দেখে। এরপর ভয়ে বিপ্লবীদের মৃতদেহ আত্মীয়ের হাতে দেয়া বন্ধ করে দেয় ইংরেজ সরকার। কানাইলাল দত্তের অস্থি ভস্ম গঙ্গা য় ফেলা হয় নি। কারণ ফেলার মত অবশিষ্ট ছিল না। বীর শহীদের অস্থিভস্ম পরম শ্রদ্ধায় সংগ্রহ করে নেন অগণিত জনতা ও বিপ্লবীগণ।
মহামৃত্যুর রুদ্র সঙ্গীত (পর্ব ৪)
আলিপুর মামলায় সরকার পক্ষের উকিল নর্তন সাহেব কে সাহায্য করছেন উকিল আশুতোষ বিশ্বাস। নরেন গোস্বামী হত্যা মামলায় তিনি ই সরকার পক্ষের উকিল । মামলায় কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ফাঁসী হয়ে গেলো। বিপ্লবীদের গোপন সভায় ঠিক হলো আশুতোষ কে মৃত্যুদন্ড দেয়া হোক। তার কাজ বিপ্লবের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। রায় কার্যকর করার দায়িত্ব পড়লো চারুচন্দ্র বসুর উপর। 22 বছরের বিবাহিত যুবক চারু একটি প্রেসে কাজ করে। স্ত্রী কিরণবালা 13 বছর বয়সী। চারুর ডানহাতের আঙ্গুলপঙ্গু। কুছ পরোয়া নেই। 10 ই ফেব্রুয়ারি 1909 এক বিষণ্ণ বিকেল। রোদের তীব্রতা ম্লান । সুবার্বান ম্যাজিস্টেট কোর্ট এর কর্মব্যস্ততা কমে এসেছে। নিজ সাফল্যে গর্বিত আশুতোষবাবু কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসছেন পূর্ব দিকের গেট দিয়ে। হঠাৎ একটি রোগা ছেলে তার সামনে এসে দাঁড়ালো। বাড়িয়ে দিল ডান হাত। ডানহাত এর আঙ্গুল পঙ্গু থাকায় সেই হাতের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা রিভলবার। বাঁ হাত ট্রিগার টিপল। গুলি খেয়ে পালানোর চেষ্টা করলে তাকে তাড়া করে দ্বিতীয় গুলি ছুঁড়লেন চারু। মৃত্যু নিশ্চিত হলো । আশুতোষ এর এবং নিজের ও। কোর্ট চত্বরে থাকা কনস্টেবল রা ছুটে এলো। শান্ত ভাবে ধরা দিলেন চারু। কার নির্দেশে এ কাজ চারু করেছে ও বিপ্লবী কর্মকান্ডের আরো খবর জানার জন্য অকথ্য অত্যাচার করা হলো জেলে। দেয়া হলো ইলেকট্রিক শক ও। কিন্তু চারুর মুখে বৃক্ষের নীরবতা। অবশেষে 29 শে মার্চ ইতিহাসের স্বর্ণজ্বল পৃষ্ঠায় চারুকে বরণ করে নেয়া হলো ফাঁসীর দড়ি পরিয়ে। মৃত্যুর আগে তিনি চিঠি লেখেন দুই দাদা ও শ্যালক কে। দেখাও করেন তাদের সঙ্গে। শ্যালক ছত্রপতি ঘোষ কে লিখেছিলেন ” অভাগা জীবনের এই শেষ পত্র। আর নয় দিন পর আমার অস্তিত্ব জগৎ হইতে লোপ পাইবে। তাহাতে আমি দুঃখিত নই। কেবলমাত্র একটি কারণে দুঃখিত। একটি অভাগিনী তেরো বৎসর বয়স্কা বালিকাকে দীন হীনা অবস্থায় এই সংসার সমুদ্রে ভাসাইলাম।…তাহার প্রতি যেন আপনাদের দৃষ্টি থাকে।” আশুতোষ হত্যাকাণ্ডের পাঁচ ছয় দিন পূর্বে তিনি বগুলায় নিজের বাড়ি গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা করে আসেন। তার দুই দিন আগে কলকাতার hop sing স্টুডিও তে একটি ছবি তুলেছিলেন। সে ছবি নিশ্চয়ই স্ত্রী কিরণের হাতে দিয়ে চির বিদায় নিয়েছিলেন এই বীর সন্তান । মৃত্যুর পূর্ব মুহুর্তে নির্ভীক চিত্তে তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ‘ বন্দে মাতরম‘।
মহামৃত্যুর রুদ্র সঙ্গীত (পর্ব ৫)
1915 সালের 9 ই সেপ্টেম্বর। উড়িষ্যার বালেশ্বর। যতদূর চোখ যায় শুধু বালি মিশ্রিত মাটি। মাঝে মাঝে অল্প কিছু গাছ। পাঁচ বীর একত্রিত। সংকল্পে শক্ত চোয়াল। সামনে বিরাট সশস্ত্র ইংরেজ বাহিনী। তিন দিন ধরে খাওয়া জোটেনি। আশ্রয় নেই। ভয়াল খরস্রোতা নদী সাঁতরে পেরোতে হয়েছে। মাঝিরা পার করে দেয় নি। কারণ আতঙ্ক। সাহেব অফিসার এসে শাসিয়ে গেছে বিপ্লবীদের সাহায্য করা মানেই মরণ কে নিমন্ত্রণ করা। ক্ষুধার্থ, আশ্রয়হীন , বলহীন পাঁচ যুবক বুক চিতিয়ে লড়ছে বিপুল ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে। একটি গুলি এসে লাগলো চিত্তপ্রিয়র দেহে। চিত্তপ্রিয় বুঝলেন মৃত্যু আসন্ন। মরণ জয়ী বীরের শেষ বাক্য ” আমার কর্তব্য শেষ। দাদাকে বাঁচাও ।” দাদা হলো যতীন মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) যিনি শুধু নেতা নন। সাথীদের প্রানের বনফহু, আত্মার আত্মীয়। বন্দুক ছেড়ে চিত্তপ্রিয়র মাথাটি কোলে নিলেন যতীন। পরম আদরে ভরিয়ে তুললেন শহীদের জীবনের শেষ অঙ্কটি। শেষ নিঃশ্বাস পড়তেই আবার হৃতশাবক বাঘিনীর মত তুলে নিলেন বন্দুক। উপযুক্ত জবাব দিতে দিতে হলেন গুলিবিদ্ধ। রক্তস্নাত দেহে গ্রহণ করলেন অন্তিম শয্যা ভারত মায়ের কোলে। অস্ফুটে বললেন ‘ জল‘। যতীন কে জল খাওয়াতেই হবে। শুশ্রূষাও দরকার তাঁর। তাই লড়াই থামিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন নীরেন, মনোরঞ্জন ও জ্যোতিষ। মনোরঞ্জন আহত। তবু ছুটলেন নদীর দিকে। চাদর ভিজিয়ে জল এনে খাওয়ালেন যতীন কে। যতীন পুলিশ সাহেব কে বললেন “এসবের জন্য আমি একাই দায়ী। এরা নির্দোষ। আমার আদেশ পালন করেছে মাত্র।” মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও যতীন আদর্শ নেতার মত সব দায় নিজের কাঁধে নিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করলেন সাথীদের। তবু শেষ রক্ষা হলো না। বিচারে নীরেন ও মনোরঞ্জনের ফাঁসী হলো। জ্যোতিষ দণ্ডিত হলেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে। পরবর্তী তে পুলিশের অত্যাচারে মানসিক রোগের শিকার হয়ে তিনি বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত হন। সেখানে সকলে শুনতো জ্যোতিষ প্রায় ই দাদা দাদা বলে চিৎকার করছে আর জেলের দেওয়ালে দেওয়ালে বাঘা যতীন এর জীবন ও কাজ লিখে রাখছে। দেশমাতার বীর সন্তান যতীন শুধু তাঁর সাথীদের হৃদয়েই নয়, অগণিত ভারতবাসীর হৃদয়েই নয় তার সীমানা পেরিয়ে শত্রু ইংরেজ অফিসার মি: টেগার্টের হৃদয়েও চির স্থান করে নিয়েছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে টেগার্ট বলেছিলেন ” though I had to do my duties, I have a great admiration for him. He was the only Bengali, who died in an open fight from a trench ‘ এখানেই মৃত্যু ও মহামৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য। মৃত্যু জীবনের শেষ আর মহামৃত্যু জন্ম দেয় এক অনন্ত জীবনের।
মহামৃত্যুর রুদ্র সঙ্গীত (পর্ব ৬)
১৯১৫ সালের ৩০ শে এপ্রিল দৌলতপুর থানা। পুলিশ বাবুরা এক প্রস্থ ভাত ঘুম দিচ্ছেন। এমন সময় হন্ত দন্ত হয়ে এসে খবর দিলো এক যুবক। প্রাগপুরে হরিনাথ সাহার দোকানে ডাকাত পড়েছে। যেমন তেমন ডাকাত নয়। স্বদেশী ডাকাত। উড়ে গেল ভাতঘুম। পড়ি মরি করে ছুটলো পুলিশের দল। ততক্ষনে ডাকাতি প্রায় শেষ করে ফেলেছেন সুশীল সেন, ফনী রায়, ক্ষিতীশ সান্যাল, আশুতোষ লাহিড়ী ও গোপেন্দ্রলাল রায়। ডাকাতির অর্থ বিপ্লবের কাজে লাগবে। অগণিত দেশবাসীর শৃঙ্খল মোচনের উপায় এই অর্থ। পালানোর পথে ঘিরে ফেললো পুলিশ। চললো গুলি। প্রত্যুত্তর দিলেন বিপ্লবীরাও। ভেঙে গেল ব্যারিকেড। পালাতে সক্ষম হলেন বিপ্লবীরা। শুধু একটি গুলি এসে লাগলো সুশীলের পা এ। বহু কষ্টে সাথীদের কাঁধে ভর দিয়ে চলতে চলতে খলিলপুর চরের কাছে এলেন তাঁরা। আর এগোনো যাচ্ছে না। মাটিতে পড়ে গেলেন সুশীল। সাথীদের বললেন ” আমাকে নিয়ে তোমরা বিপদে পড়বে। আমাকে মেরে মুন্ডু টা কেটে নাও তোমরা ; যাতে পুলিশ আমার দেহ সনাক্ত করতে না পারে। তারপর আমার দেহ টা ডুবিয়ে দাও নদীর জলে। ” সুশীলের প্রস্তাব শুনে থমকে গেলেন সাথীরা। তাঁদের তামসিকতা কাটানোর জন্য গর্জে উঠলেন সুশীল ” সময় অল্প। জলদি করো। আমাকে বাঁচানোর থেকেও জরুরী দেশ কে বাঁচানো। ” নিরুপায় সাথীগণ মেনে নিলেন বীর সুশীলের আদেশ। কেটে নিলেন মুন্ডু। হারিয়ে গেল সুশীলের মুণ্ডুহীন লাশ নদীর অতল জলে। জগতের সামনে যুদ্ধক্ষেত্র বা ফাঁসীর মঞ্চে নয়। নিভৃতে সকলের অলক্ষ্যে দেশের স্বার্থে আত্মবিলোপ সুশীল সেনের মৃত্যু কে মহিমান্বিত করে তোলে। সুশীল কে অনুসরণ করে এক ই পথে অগ্রসর হন খুলনার যুবক সুরেন কুশারী। ১৯১৭ সালের ৭ ই মে রাত্রি ৯ টায় বিপ্লবের অর্থ সংগ্রহ করতে এক সোনার দোকানে ডাকাতি করতে গিয়ে আহত হন সুরেন। তলপেটে গুলি লাগে তাঁর। পালানো অসম্ভব বুঝে তাঁর দুই সাথীকে সুরেন নির্দেশ দেন তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলার জন্য। সুরেনের স্বপ্নীল দুচোখ কে ঘুম পাড়িয়ে দেন দুই সাথী সুরেনের স্বপ্ন কে জাগিয়ে রাখার জন্য। একটি বড় গাছের নিচে শহীদের মৃতদেহ কে শুইয়ে রেখে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যান আলোর পথযাত্রীদ্বয়।
মহামৃত্যুর রুদ্রসঙ্গীত (পর্ব ৭)
প্রবল শীতে শরীরটা কুঁকড়ে আছে। দুচোখে ঘুম নেই। পরিত্যক্ত মালগাড়ির কামরা টা যেন বরফশয্যা। বাইরে উঁকি দিতেই ভোরের হিম শীতল বাতাস মুখে লাগলো। আঁধার সরে আকাশ ফর্সা হচ্ছে। শুনশান চারিদিক। এবার পালাতে হবে। আসামের আটগাঁ এর কাছে নবগ্রহ পাহাড়ের তুমুল সংঘর্ষে পুলিশ এর ব্যারিকেড ভেঙে পালিয়ে এসেছেন নলিনী বাগচি। পুলিশ তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। আলো আঁধারীতে হাটতে হাটতে ডেহিং নদীর কাছে এসে পড়েছেন। নদী পেরিয়ে বহু কষ্ট ও বিপদের মধ্যে দিয়ে নলিনী কলকাতায় পৌঁছলেন। অবাক লাগছে নিজের ই। পুলিশ এর চোখে ধুলো দিয়ে এতো টা পথ এলেন কি করে ? এখন গন্তব্য গোপন ডেরা। গড়ের মাঠে একটা গাছের তলায় বসলেন নলিনী। শরীর বিধ্বস্ত। মাথা ঘুরছে। কপালে হাত দিয়ে বুঝলেন প্রবল জ্বর। আর ওঠার সামর্থ নেই। একি !! গা এ গুটি গুটি কি সব বেরিয়েছে যেন ? নলিনী বুঝলেন তিনি বসন্তে (pox) আক্রান্ত। শুয়ে পড়লেন গাছের তলায়। প্রতীক্ষা মৃত্যুর। চারপাশ টা কালো হয়ে আসছে। আহা কি শান্তির মৃত্যু। – ‘আরে নলিনী না ?’ অন্ধকারে আবছা বোঝা গেলো মুখ টা। অনাথবন্ধু ঘোষ। বন্ধু নলিনী কে চিনতে পেরেছেন অনাথ। ডাকলেন সতীশ পাকরাশী কে। দুই বন্ধু মিলে সেবা করে সারিয়ে তুললেন নলিনী কে। সুস্থ হয়ে নলিনী সজল নয়নে বিদায় নিলেন দুই বন্ধুর নিকট। এসে উঠলেন ২৮ নম্বর কলতাবাজার স্ট্রীট এ এক বাড়িতে। সেখানে থাকেন আরো দুই বিপ্লবী। তারিণীপ্রসন্ন মজুমদার ও হরিপ্রসন্ন দে। একদিন গভীর রাতে পুলিশ ঘিরে ফেললো বাড়ি।পুলিশের হুঙ্কার, “সারেন্ডার” । ভেতর থেকে কোনো উত্তর এলো না। অখন্ড নীরবতা। পুলিশ জোর করে বাড়ির ভিতরে ঢুকলো। শুরু হলো তুমুল লড়াই। পুলিশ অফিসার বসন্ত মুখার্জি গুরুতর আহত হলেন। নিহত হলেন পাতিরাম সিং। এই যুদ্ধে সাংঘাতিক আহত হন নলিনী বাগচি। হাসপাতালে পরের দিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুর আগে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করতে এলে পুলিশ কে তিনি বলেন ” Don’t disturb me Let me die peacefully. ” নলিনী র অনবদ্য জীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয় সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় এর বিখ্যাত সেই উক্তি ” সেদিন অস্ত্র হাতে করার মধ্যে প্রাণ নেওয়ার কথাটা বড় ছিল না। প্রাণ দেয়ার কথাটাই ছিলো বড়। একটি প্রাণ বলিদানে সহস্র প্রাণ জেগে উঠবে এই ছিলো কামনা।“
মহামৃত্যুর রুদ্র সঙ্গীত ( পর্ব ৮)
রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ ও ভয়ঙ্কর অলিন্দ যুদ্ধ ইংরেজ এর দম্ভ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফানুস একেবারে চুপসে দিয়েছে। বাংলার তিন দামাল ছেলে নাড়িয়ে দিয়েছে ব্রিটিশ দুর্গের ভিত। বিনয়, বাদল, দীনেশ। action শেষ করে আরাম করে একটি বেঞ্চে পাশাপাশি বসে তিনজনেই নিজ নিজ কপালে গুলি চালালেন। এ যেন মেলা দেখতে বেরিয়ে তিন বন্ধু একসঙ্গে নাগরদোলা (মরণ দোলা ?) চাপছেন। বিনয় বেঁচে গিয়েও পরে হাসপাতালে মারা যায়। বাদল সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়। দীনেশ গুপ্ত হাসপাতালে সুস্থ হয়ে ওঠেন। তাঁর ফাঁসী হয় ৭ই জুলাই ১৯৩১ সালে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। পরের দিন আনন্দ বাজার পত্রিকায় খবর বেরোলো, “বিশ বছরের দীনেশ ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিলো যেমন ব্যগ্র বালক তার খেলনার দিকে হাত বাড়ায়।” মৃত্যুর আগে তাঁর ওজন বেড়ে যায়। ফাঁসুড়ে শিবু ডোম বলেন ” তিনি অদ্ভুত মানুষ। ফাঁসির আগে পর্যন্ত আমার সঙ্গে রসিকতা করছিলেন ।” দীনেশের মধ্যে ছিল না কোনো ভয় বা অনুতাপের চিহ্ন। ১৭ ই মার্চ তিনি ক্ষোভ ভরে লিখেছেন ” বিয়ে আর চাকরির চিন্তাই বাঙালির অস্থি মজ্জা কে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।….তারা বড় বড় কথা বলে আর কাজের সময় বৌ এর আঁচলের তলায় লুকোয়।“
মৃত্যুর ৬০ দিন আগেও তিনি বলেছেন “আমি অমৃতের সন্তান, তিনি সত্য , চিরপ্রেমে আমি তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া থাকিতে চাই।” মহামৃত্যুর ২১ দিন আগে চিঠিতে জানাচ্ছেন দীনেশ ” মুক্তির দিন আসিয়াছে, আনন্দের কথা, কিন্তু তবু দুঃখ হয় মায়ের চোখের জল, বুক ভরা ক্রন্দন দেখিয়া।” দেশ জননীর পায়ে উৎস্বর্গীকৃত মাতৃগতপ্রান দীনেশ গর্ভধারিনী মা কে ফাঁসীর এগারো ঘন্টা আগে তাঁর যে শেষ চিঠি লেখেন তা পড়ে চোখের জল আটকে রাখা যায় না। বিকেল সাড়ে পাঁচ টায় অস্তাচলগামী সূর্যের ক্ষীণ আলোয় লেখা সেই চিঠি ” মা তোমার সঙ্গে আর দেখা হইবে না, কিন্তু পরলোকে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিব। তোমার জন্য কিছুই কোনদিন করিতে পারি নাই। সে না করা যে আমাকে কতখানি দুঃখ দিতেছে তাহা কেহ বুঝিবে না, বুঝাইতে চাইও না।” চলে যাবার দিন দীনেশ খুব হাসিখুশি ছিলেন। আগের দিনের বিষণ্ণ ভাব আর সেদিন ছিল না। শিবু ডোম এর সঙ্গে রসিকতা ও করছিলেন। শেষ সময়ে মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ‘বন্দে মাতরম‘ ধ্বনি দিলেন। দ্বিতীয় বার ধ্বনি সম্পূর্ণ হলো না। তার আগেই সরে গেল পায়ের নিচের কাঠ টা।
মহামৃত্যুর রুদ্র সঙ্গীত (পর্ব ৯)
১২ই জানুয়ারি ১৯৩৩ সাল। কুয়াশার চাদর ঢাকা পৌষের ভোরে জেলের ভিতর নিজের সেলে প্রতিদিনের মত ব্যায়াম করছেন এক তেজস্বী যুবক। প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য্য। আজ ই তাঁর ফাঁসির দিন। গত কাল বিকেলেও তিনি স্বচ্ছন্দে ঘোরা ফেরা করেছেন। রাতে সকলে শুনেছে প্রদ্যুৎ উচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি করছে
” অত চুপি চুপি কেন কথা কও
মরণ , ওগো মরণ “।
ব্যায়াম শেষ। এবার গরম জলে স্নান করলেন নিজে। তারপর আরাম করে বসলেন গীতা পাঠ করতে। দেখতে দেখতে ভোর সাড়ে পাঁচ টা বাজলো। সেলের তালা খুলছে ঘাতক প্রহরী। গীতা যথাস্থানে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে প্রদ্যুৎ বললেন, “ঠিক হ্যায়“। অন্যান্য সেলের বিপ্লবীরাও জেগে। আকাশ বিদীর্ন করে আওয়াজ উঠলো “প্রদ্যুৎ কুমার কি জয়।“
ভোর ছটা বাজছে। ফাঁসির মঞ্চের কাছে আনা হলো প্রদ্যুৎ কে। জেলাশাসক বার্জ নিচে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন-“are you ready pradyut ?” প্রদ্যুৎ উত্তরে জানালেন “হ্যাঁ“। ক্ষণিক নীরবতা । তারপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন প্রদ্যুৎ “We are determined Mr. Burge not to allow any European to remain in Midnapore. Yours is the next turn get yourself ready”. সাহেবের মুখ শুকিয়ে গেল। রুমাল দিয়ে ঘাম মুছল সাহেব। ফাঁসিমঞ্চে দাঁড়িয়েও জেলাশাসক বার্জ কে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে বললেন প্রদ্যুৎ। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও তিনি সংগ্রাম কে ভুলে যান নি। তাঁর কথা রেখেছিলেন সাথীরা। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁরা নিকেশ করে দিয়েছিলেন অত্যাচারী বার্জ কে । মৃত্যুর কয়েকদিন আগে গর্ভধারিনী মা কে চিঠি লিখেছেন বীর প্রদ্যুৎ। সে চিঠিতে গর্ভধারিনী মা আর দেশ মা যেন এক হয়ে গেছে। সে চিঠি বিদ্রোহের রণ হুঙ্কার – ” ….যুগ যুগ ধরে তুমি যে অপমান লাঞ্ছনা ও নির্যাতন সহ্য করে এসেছ, মাটিতে মুখ থুবড়ে বোবা গরুর মত মার খেয়েছ, তার বিরুদ্ধে তোমার মনে যে বিদ্রোহের ধারা অন্তসলিলা ফলগুর মত বয়ে যাচ্ছিল সেই পুঞ্জীভূত বিদ্রোহ ই তো আমি। সেই বিপ্লব যদি আজ আত্মপ্রকাশ করে তবে তার জন্য চোখের জল ফেলবে কেন ?…..মা তোমার প্রদ্যুৎ কি কখোনো মরতে পারে ? আজ চারিদিকে চেয়ে দেখো লক্ষ লক্ষ প্রদ্যুৎ তোমার দিকে চেয়ে হাসছে। আমি বেঁচেই রইলাম মা, অক্ষয় অমর হয়ে— বন্দে মাতরম “।
মহামৃত্যুর রুদ্র সঙ্গীত (পর্ব ১০)
চুউউউপ। silence. আদালতের রায় বেরিয়ে গেছে। ঐ তো নিয়ে আসা হচ্ছে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য কে। পা এ বারফেটাস (ডান্ডাবেড়ি)। কিন্তু পা এ বারফেটাস তো বিশেষ সাজার লক্ষণ। চরমুগুড়িয়া হত্যা মামলায় মনোরঞ্জনের কি শাস্তি হলো জানতে উম্মুখ যুগান্তর দলের বন্ধুরা। সকলে চিৎকার করে উঠলেন ‘ কি সাজা হলো?’ নির্ভীক মনোরঞ্জন বললেন ‘ সবার সাজা হলো। আমি শুধু খালাস। বাড়ি যাবো এবার। ‘ সকলে বললো ‘ কি হলো ?’ আরো দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলেন মনোরঞ্জন ‘ বললাম তো। আমি খালাস। বাড়ি যাবো। তোমরা জেলে পচে মরো।‘ সকলে দেখলো একেবারে অন্তিম সেলে ঢোকানো হচ্ছে মনোরঞ্জন কে। ওটা কনডেমড সেল। ঐ সেলে ঢোকার অর্থ বুঝতে বাকি নেই কার ও। মনোরঞ্জন এর ফাঁসির হুকুম হয়েছে। সুদীর্ঘ সুঠাম বলিষ্ঠ চেহারা। শান্ত হয়ে সেলে ঢুকেই গান ধরলেন। রবীন্দ্রনাথ এর গান। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যেন সত্যি মুক্তি পেয়ে বাড়ি যাবার আনন্দে পাগল। বরিশাল জেলে তাঁর ফাঁসি হয়। বিপ্লবী অমূল্য নাথ মজুমদার স্মৃতিচারণ করেছেন , শেষের আগের দিন মা বাবা স্ত্রী দেখা করতে এলেন মনোরঞ্জন এর সঙ্গে। তাঁরা কথা বলছেন না। শুধু অশ্রু বিসর্জন করছেন অঝোর ধারে আর মনোরঞ্জন গীতার শ্লোক বলে তাঁদের শোক দূরীভূত করার পরামর্শ দিচ্ছেন। পরের দিন ভোর চারটের সময় শোনা গেল আকাশ বিদীর্নকারী রব ‘ বন্দে মাতরম‘। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জেলে শত কণ্ঠে একসঙ্গে ধ্বনিত হলো ‘বন্দে মাতরম‘। অমূল্য নাথ দেখলেন ফাঁসির পর লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে লাশঘরে। জমাদার কাঁদছে হাউ হাউ করে। ঘুমিয়ে আছে মনোরঞ্জন। সতেজ দেহ। মুখে প্রশান্ত হাসি। বাড়ি ফেরার আনন্দ।
মহামৃত্যুর রুদ্র সঙ্গীত ( পর্ব ১১)
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন শেষে রাতের অন্ধকারে জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছেন বিপ্লবীরা। মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে বিল্লবীরা এই কর্মসূচির নাম দিয়েছেন ‘ মৃত্যুর কর্মসূচী‘। স্বাধীনতার জন্য মৃত্যু। জল নেই। খাবার নেই। নিদ্রাহীন রাত্রি জুড়ে হাঁটতে হাটতে সকলে অবসন্ন। বিকেল বেলা পাহাড়ের পাদদেশে নিঃশব্দে এসে পৌঁছলো হায়নার দল, ইংরেজ সৈন্য। মুষ্টিমেয় বিপ্লবীদের সঙ্গে শুরু হলো তুমুল লড়াই। একে একে শহীদ হয়ে গেলেন টেগরা (হরিগোপাল বল ) , প্রভাস বল, বিধু ভট্টাচার্য। গুলিবিদ্ধ হয়ে টেগড়া বললেন ” সোনাভাই– আমি চললাম। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও। ” বিধু বার বার স্থান পরিবর্তন করে গুলি চালাচ্ছিলেন। lying down পজিশন তখন তাঁর মাথায় নেই। হঠাৎ একটি গুলি এসে বিদীর্ন করল বিধুর বুক। ঢলে পড়ার সময় চিৎকার করে প্রিয় বন্ধু নরেশ কে বললেন ” এরা আমারে হাঁদাইছে । আমি চললাম। তুমিও আইয়। ” এরপর ত্রিপুরা সেন শহীদ হলেন। তারপর স্কুল ছাত্র নির্মল লালা। সে দলে যোগ দেবার সময় বন্ধুদের বলে এসেছিল, ” আমি আর পড়বো না। কোনোদিন কক্স বাজারে ফিরবো না। মরতে চললাম। ” যুদ্ধ শুরুর আগে মাস্টারদা বলেছিলেন ‘ ছোটরা চাইলে লুকিয়ে শহরে চলে যাও। পুলিশ এর খাতায় তোমাদের নাম নেই। তোমাদের কোনো বিপদ হবে না “। নির্মল দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিল ” মাস্টারদা মরতে এসেছি। ফিরে যাবার জন্য আসিনি।” আহত হলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, অর্ধেন্দু দস্তিদার। অম্বিকা চক্রবর্তী ধরা পড়েন নি। কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন অর্ধেন্দু। পুলিশ তার চিকিৎসা না করিয়ে জেরা করতে শুরু করলো। পরদিন অর্ধেন্দু বাঞ্ছিত লোকে চলে গেলেন। মুমূর্ষু বিপ্লবী কে জেরা করেও পুলিশ কিছুই বার করতে পারে নি। শেষ সময় অবধি অর্ধেন্দু বলে গেছেন ” মাস্টারদা বলেছেন হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু। ” তেজস্বী যুবক ঘোষণা করেছিলেন ” মরার আগে ডাক্তার ছাড়া কারো হাতে জল খাবো না। ” জালালাবাদের যুদ্ধে 62 জন বিপ্লবী বিরাট প্রশিক্ষিত ইংরেজ বাহিনী কে পরাস্ত করে। জীবিত বিপ্লবী গণ সংগ্রাম অব্যাহত রাখার তাগিদে রাতের অন্ধকারে গোপন আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে অদৃশ্য হয়ে যান।
মহা মৃত্যুর রুদ্র সঙ্গীত (পর্ব ১২)
পয়লা ডিসেম্বর ১৯৩০ ভোর সাড়ে চারটে। কুয়াশার চাদর ঢেকে ঘুমিয়ে আছে চাঁদপুর শহর। মৃত্যু শীতল পরিকল্পনা বুকে নিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাস এ বসে আছেন দুই যুবক। ট্রেন এর ফার্স্ট ক্লাস এ আসছেন কুখ্যাত ক্রেগ সাহেব। চট্টগ্রাম বিদ্রোহের বন্দীদের মামলায় সাক্ষী দেবেন। চাঁদপুর স্টেশনে গাড়ি থামলো। দুই যুবক ভালো করে মুখ অবধি চাদর মুড়ি দিয়ে ফার্স্ট ক্লাস কামরার কাছে এগিয়ে এলেন। চাদরের তলায় রিভালবার। ফার্স্ট ক্লাস এর দরজা খুলতেই বেরিয়ে এল সাহেব। বেরিয়ে এলো রিভালবার বিদ্যুৎ গতিতে। ভোরের স্টেশনের নীরবতা ভেঙে গেল গুলির শব্দে। লুটিয়ে পড়ল সাহেব। মুখে আর্তনাদ ” বাবারে , মরে গেলাম“। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস হাত ধরলেন কালিপদ চক্রবর্তী র। বললেন ” ভাই , এ তো বাঙালি ! ভুল হয়ে গেল। চলো পালাই ।” ধূর্ত ক্রেগ বাঙালি পুলিশ অফিসার তারিণী মুখার্জী কে সাহেবের পোশাক পরে আগে নামতে বলেছিল। তার ই প্রাণ গেল। ধরা পড়ে গেলেন দুজনেই। শুরু হলো বিচার। রামকৃষ্ণ কালিপদ কে বললেন, “যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পচে মরার থেকে ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে মৃত্যু বরণ অনেক ভালো। এ আত্মদান হাজারো তরুনের মনে প্রেরণা জোগাবে। ” বিচারে কালিপদর যাবজ্জীবন হলো। রামকৃষ্ণের ফাঁসি। রায় শুনে বন্ধু কে জড়িয়ে ধরলেন রামকৃষ্ণ। কালিপদ বলছেন সে জড়িয়ে ধরার মধ্যে দরদ ছিল। কত খুশি। এক মুখ আলো নিয়ে বললো ” আমি খুব খুশি তুমি বেঁচে গেছো বলে। ভালো থেকো বন্ধু। ” সদাহাস্যময় প্রাণ খোলা যুবক রামকৃষ্ণ কে কেউ কখনো বিষন্ন দেখেনি। তাঁর পাশের সেলেই থাকতেন বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে কালিপদ এক ইংরেজ জেলার এর সহযোগিতায় তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা করতে যান। রামকৃষ্ণ তখন কম্বল এর উপর বসে বই পড়ছে। চারিদিকে অজস্র বই ছড়ানো। শেষ দিকে খুব পড়তেন তিনি। কালিপদ কে দেখেই তাঁর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো । বললেন ” আরে। তোমার শরীর বেশ খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। দেখো, গত তিন মাসে যা পড়লাম, শিখলাম ও জানলাম তা ফেলে আসা সারা জীবনের চাইতেও বেশি। তুমি পড়াশুনা করবে। দু একটা ভাষাও শিখতে চেষ্টা কর। পড়াশুনা করে জীবনের সময় টুকু কাজে লাগাবে।” বন্ধুর চোখে জল। মনে মনে ভাবছেন এ পড়াশোনা তার কি কাজে লাগবে ?…পরমুহূর্তেই ধাক্কা খেলেন। তাঁর পড়াশোনা তো কাজে লাগানোর জন্য নয়। চেতনার উত্তরণের জন্য। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে জীবন শেষের আগে সঠিক জীবনবোধ অর্জন করার জন্য তাঁর পড়াশোনা। এই মহান বিপ্লবীর বোন পরিচয় দিয়ে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার তাঁর সঙ্গে ফাঁসির পূর্বে চল্লিশ বার দেখা করেন। তাঁর জীবনদর্শন প্রীতিলতা কে মুগ্ধ করে। প্রীতিলতা বলছেন ” ….মৃত্যু অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য। তিনি মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমান ছিলেন না। তাঁর উচ্ছ্বাস, হাসি, কবিতাপ্রিয়তা সব কিছুর প্রাণ প্রাচুর্যে তিনি ভরিয়ে রেখেছিলেন ফাঁসি–সেল। কিন্তু তাঁর ও কিছু আক্ষেপ ছিল, তিনি প্রায় ই বলতেন এখনও কত কাজ বাকি রয়ে গেল । “
মহামৃত্যুর রুদ্র সঙ্গীত (পর্ব ১৩)
১৯৩২ সালের ১৩ ই জুন ধলঘাট গ্রামের এক মাটির দোতলা বাড়ি। সবাই সাবিত্রী মাসির বাড়ি বলেই চেনে। দুদিন আগে থেকেই সেখানে অজ্ঞাত বাসে আছেন মাস্টারদা সূর্য সেন ও নির্মল সেন। বিপ্লবী অপূর্ব সেন (ভোলা) সেখানে প্রীতিলতা (রানী) কে নিয়ে এলেন। মেধাবী ছাত্রী রানী। মাধ্যমিক এ মেয়েদের মধ্যে প্রথম, সকলের মধ্যে পঞ্চম। বেথুন কলেজ থেকে স্নাতক পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ। কিন্তু মনে দেশের জন্য প্রাণ দেয়ার উদগ্র বাসনা। মাস্টারদা ও নির্মল দার নয়নের মনি সে। এলেই কত গল্প, বিপ্লবের আলোচনা আর গুলি ছোঁড়ার ট্রেনিং। রানী বার বার আবেদন করে তাকে কোনো শসস্ত্র অ্যাকশন এ সঙ্গে নিতে হবে। ভোলা সরল অকপট ছেলে। ছোট ছোট কথা তেও প্রাণ খুলে হাসে। বিপ্লবীদের দুঃখ সইবার ক্ষমতা যেমন অসীম তেমন ই অসীম জীবনের ছোট ছোট ঘটনা থেকে আনন্দ নেবার ক্ষমতাও। সকলের জন্য রান্না করল রানী। রান্নার সময় দাদাদের সঙ্গে কত হাসি মজা। যেন আনন্দের হাট। রাত হলো। খেতে বসার সময় নির্মল দা জানালেন খিদে নেই, আজ খাবেন না। ওপরে গিয়ে শুলেন। রানী গেল প্রিয় দাদা কে সেধে খেতে রাজী করাতে। ওপরে উঠে নির্মলদা কে অনুরোধ করছেন। এমন সময় মাস্টারদা তীর বেগে ছুটে এসে বললেন, পুলিশ পুলিশ। বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। রানী বললো আমি আপনাদের সঙ্গেই থাকবো। মাস্টারদা বললেন নিচে যাও। নিজেকে সাবিত্রী মাসির আত্মীয় বলে পরিচয় দাও। নিচে চলে গেল রানী। বাইরের সিঁড়ি দিয়ে তখন রিভলবার হাতে উঠে আসছেন ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন। সিঁড়ি থেকেই গুলি ছুড়লেন নির্মল দা। গড়িয়ে পড়ে গেল ক্যামেরুন। শুরু হয়ে গেল বিপ্লবী দের সঙ্গে পুলিশ এর গুলির লড়াই। গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম। হঠাৎ নির্মল দার চিৎকার। তিনি গুলিবিদ্ধ হলেন। মৃত্যুর পূর্বে রানী রানী বলে ডাকতে লাগলেন। কি বলতেন তিনি রানী কে ?….ডাক শুনে দাদার কাছে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করলো রানী। কিন্তু সকলে তাকে জাপটে ধরে রাখলো। বড় আফসোস রয়ে গেল শেষ সময়ে দাদার পাশে যেতে না পেরে। ইতিমধ্যে নিচে নেমে এলেন মাস্টারদা ও ভোলা। ভোলা তখন ও হাসছে। ওই বিপদেও সে নির্বিকার। মাস্টারদা কে রক্ষা করাই তখন তার ধ্যান জ্ঞান। রানী মাস্টারদা কে বললো আপনার সঙ্গে যাবো, দয়া করে সঙ্গে নিন। মাস্টারদা বললেন চলো। তারা বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বেরোলেন। ঘুট ঘুটে অন্ধকার। এমন সময় শুকনো পাতায় পা লেগে আওয়াজ উঠলো। আওয়াজ লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল এক পুলিশ। গুলি লাগলো ভোলার বুকে। তার নিথর দেহ পড়ে রইলো অন্ধকারে। সামনে দূষিত জলের পানা পুকুর। সেখানে ডুব দিলেন রানী আর মাস্টারদা। শুধু নাকটা জলের ওপরে। পুলিশ তাদের খুঁজে না পেয়ে চলে গেলে তারা উঠে অন্য গোপন ডেরার দিকে এগোলেন। এই রানী মাষ্টারদার নির্দেশে 24 সে সেপ্টেম্বর ১৯৩২ সালে পুরুষের পোশাক পরে পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের দুঃসাহসিক অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সফল নেতৃত্বে অ্যাকশন কার্যকরী করার পর যোগ্য নেতার মত সকলকে আগে নিরাপদে পাঠিয়ে নিজে চলেছিলেন শেষে। শেষ রক্ষা হলো না। পেছন থেকে আসা এক গুলির আঘাতে গুরুতর আহত হলেন রানী। ধরা দেবেন না পন করেছিলেন। সঙ্গে ছিল পটাসিয়াম সায়ানাইড । পুলিশের নাগালের বাইরে চলে গেলেন মুহূর্তে। চলে গেলেন আমাদের ও নাগালের বাইরে। সকল বিপ্লবীরা সজল নয়নে কাট্টলী গ্রামে পৌঁছে মাস্টারদা কে নিদারুন সংবাদ দিলেন। তাঁরা বললেন, ” কাজ সাফল্যমন্ডিত। কিন্তু রানী আমাদের ছেড়ে চলে গেছে“। প্রীতিলতা ভারতের দ্বিতীয় লক্ষীবাঈ। নারী সশক্তি করণ, (women empowerment) নিয়ে আমরা এত কথা শুনি। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এর জীবন আমাদের দেখিয়ে দেয়– মেয়েরা ছেলেদের সমান নয়। বরং তারা ছেলেদের অনেক ওপরে। তারা স্বয়ং দশভুজা। একদিকে মাতৃত্ব, অন্যদিকে অসুর নাশিনী যোদ্ধৃবেশ। প্রনাম।





























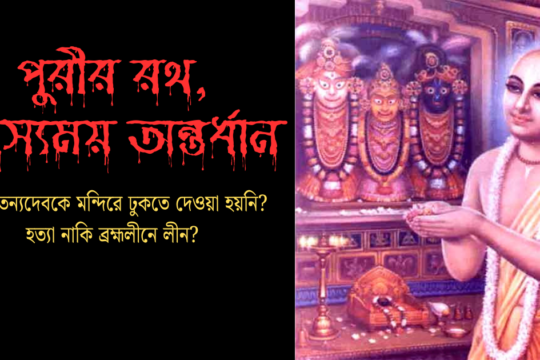

অনেক অজানা ইতিহাস জানতে পারলাম।